২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬
নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কোন বাহিনী খুব একটা বেশি দেখা যায় না। তবে নদী-কেন্দ্রিক বাহিনীর ইতিহাস পৃথিবীতে কম নয়। বিশেষ করে নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠার স্থানগুলিতে এরকম বাহিনীর আবির্ভাব দেখা গেছে বেশ নিয়মিতই। তবে নদী থাকলেই যে নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী থাকবে, তা কিন্তু নয়। বাহিনীর দরকার হয়েছে সর্বদাই রাজনৈতিক কারণে। রাজনীতিই নদীকে খুঁজে পেয়েছে শক্তি এবং সম্পদ গড়ার কেন্দ্রে। আর সেখানেই শুরু হয়েছে নদী নিয়ে টানাটানি। নদী মানেই পানি; আর পানি মানেই শক্তি। সেই শক্তি নিয়েই রাজনীতির খেলায় নদী পরিণত হয়েছে সামরিক কর্মকান্ডের উতসভূমিতে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপের দানিয়ুব নদীর কথা বলা যায়। বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, জার্মানি – এই সব দেশগুলিই এই নদীর পানিতে সিক্ত হয়েছে, এবং ইতিহাসের অনেক বড় বড় রাজনৈতিক এবং সামরিক সঙ্ঘাত এই নদী বরাবর সংঘটিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্ববহ হওয়ায় এবং একে একটা শক্ত ভৌগোলিক বাধা হিসেবে চিন্তা করার কারণে অনেক রাজনৈতিক শক্তিই এই নদীকে মানচিত্রে খুঁজে ফিরেছে। নদী হয়েছে রাজনৈতিক শক্তিকে ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট আকৃতি দানের সীমানা প্রাচীর। যে নদী এই প্রাচীর রচনা করেছে বা প্রাচীর দিয়ে যে নদীকে কাটাকুটি করা হয়েছে, সেখানেই রাজনীতির খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। ইন্দোচীনের মেকং নদী, ভারতীয় উপমহাদেশের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র, আফ্রিকার নীলনদ, উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স এবং হাডসন নদী, দক্ষিণ আমেরিকার পারানা-প্যারাগুয়ে-উরুগুয়ে-রিও ডে লা প্লাটা নদী – এরকম বেশ কিছু উদাহরণ দেয়া যাবে, যেখানে রাজনৈতিক সীমানা নদীকে কেন্দ্র করে বা নদীকে উপেক্ষা করে তৈরি করা, যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে নদীকে নিয়ে হয়েছে সংঘাত।
রাজনৈতিক সীমানা নদী থেকে সড়ে গেলেই আবার সেখান থেকে সংঘাত চলে গেছে – এমন উদাহরণও রয়েছে। যেমন, বর্তমান পোল্যান্ডের সীমানা মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও পোল্যান্ডের সীমানা বর্তমান বেলারুশের অনেকটা ভেতরে ছিল। একারণে প্রিপইয়াত নদীর বেশ কিছু অংশ এবং তার সাথে প্রিপইয়াত জলাভূমির কিছু অংশ পোল্যান্ডের অধীন ছিল। ১৯২০-এর দশকে পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ করে; আর সেই যুদ্ধের কেন্দ্রে থাকে প্রিপইয়াত জলাভূমি। এই জলাভূমি আমাদের দেশের হাওড় অঞ্চলের মতো। সেখানে অন্য কোন যোগাযোগের পদ্ধতি না থাকায় পোল্যান্ড ‘রিভার ফ্লোটিলা’ বা নদী-কেন্দ্রিক নৌবাহিনী তৈরি করেছিল। এরকম জলাভূমিতে যুদ্ধ করা খুব কষ্টকর বলেই সোভিয়েতরা সুযোগ বুঝে ১৯৩৯ সালে জার্মানরা পোল্যান্ড আক্রমণ করার সময়ে প্রিপইয়াত নদীর পুরোটা দখলে নিয়ে ফ্রন্টলাইন আরও পশ্চিমে ঠেলে দিয়ে বাগ নদীতে নিয়ে আসে। আজকের দিন পর্যন্ত সেই বাগ নদীই পোল্যান্ড এবং বেলারুশের সীমানা। প্রিপইয়াত জলাভূমি পুরোটাই বেলারুশের। কাজেই পোল্যান্ডের রিভার ফ্লোটিলাও আজ নেই।
 |
| কলম্বিয়ার নৌবাহিনীর Patrullera
de Apoyo Fluvial (PAF) or Riverine
Support Patrol Boat পৃথিবীর সবচাইতে অন্যরকম যুদ্ধজাহাজের একটি। উপরের
ডিজাইনটি এর চতুর্থ জেনারেশনের সংস্করণ। বর্মাবৃত এই জাহাজ ছোট ছোট বোটের
এসল্ট ইউনিটকে সাপোর্ট দেয়। |
কলম্বিয়ার জঙ্গলে…
তবে পুরো নদী নিজের দেশের ভেতরে থাকলেই যে সেখানে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই, তা কিন্তু নয়। সংঘর্ষের কারণ নদী না হলেও সংঘর্ষ নদীকে কেন্দ্র করেই হতে পারে। তখন রাজনৈতিক কারণেই নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী তৈরি করা লাগতে পারে। সবচাইতে চমতকার উদাহরণ হলো কলম্বিয়া। প্রায় ছয় দশক ধরে কলম্বিয়াতে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী গোষ্ঠীর আবির্ভাবের কারণে কলম্বিয়া নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী গঠনের এক্সপার্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৬ সালে গঠন করা হয় Flotilla Avispa (Wasp Flotilla), যা কিনা কলম্বিয়ার নদী-কেন্দ্রিক বাহিনীর মূল। গত ছয় দশকে এই বাহিনী কখনোই ভেঙ্গে ফেলা হয়নি, বা এর শক্তিকে কমিয়ে ফেলা হয়নি। বর্তমানে কলম্বিয়ার রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যারিন ফোর্স (সদস্যসংখ্যা ২৩,০০০-এর উপরে) এবং পৃথিবীর সর্ববৃহত ‘রিভারাইন ফোর্স’ বা নদীকেন্দ্রিক বাহিনী। কলম্বিয়ার ম্যাগডালেনা নদী কলম্বিয়ার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হলেও এই নদী বরাবর জঙ্গী গোষ্ঠীরা অবস্থান নেয়ায় এই নদীকে রক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। এর উপরে আবার রয়েছে রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণকারী নদী, যেগুলিকে নিয়ে কলম্বিয়া সংঘাতে জড়িয়েছে আরও আগে থেকে। ১৯৩২ সালে কলম্বিয়ার সাথে পেরুর সীমানা যুদ্ধ হয়, যা Leticia Conflict নামে পরিচিত। পেরু কলম্বিয়ার দুর্গমতম অঞ্চলের কিছু অংশ দখল করে নেয়। উদ্ভট রকমের সীমানা হওয়ায় কলম্বিয়ার পক্ষে তার পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমানা রক্ষা করা ছিল অসম্ভবের কাছাকাছি; পেরুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেরকমই ছিল। উভয় দেশের কাছেই তাদের ওই দুর্গম সীমানা রক্ষার্থে একমাত্র পদ্ধতি ছিল নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী। কিন্তু তাদের দেশের অভ্যন্তর থেকে ওই নদীগুলিতে কিছুই পাঠানো যায় না!! সেই নদীতে জাহাজ পাঠানোর একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে আমাজন নদী, যা কিনা ব্রাজিলের অধীনে। অর্থাৎ উভয় দেশই ব্রাজিলের কাছে অনুমতি চেয়েছে আমাজনের ভেতর দিয়ে তাদের যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর জন্যে! কাজেই এদের সংঘাতের চাবি ব্রাজিলের হাতে ছিল অনেকটা। পেরু আমাজন নদীর মোহনায় পাহাড়া দিয়েছে, যাতে কলম্বিয়ার জাহাজ আমাজনের ভেতর দিয়ে গিয়ে কলম্বিয়া-পেরু সীমানা পর্যন্ত না পৌঁছে। পেরু সেসময় কলম্বিয়ার চাইতে সামরিক দিক থেকে বেশি শক্তিশালী থাকায় কলম্বিয়া বিরাট সমস্যায় পড়েছিল। তবে তারা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে।
কলম্বিয়া নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী গঠনে বেশ নতুন নতুন কিছু চিন্তার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। তাদের ডিজাইন এবং তৈরি করা Patrullera de Apoyo Fluvial (PAF) or Riverine Support Patrol Boat একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। একেবারেই অগভীর পানিতে (২.৫ ফুট থেকে প্রায় ১.৩ ফুট) চলতে সক্ষম এই জাহাজগুলি জবরজং বর্মে মোড়া, শক্তিশালী অস্ত্র বহণ করে, এমনকি হেলিকপ্টার নামার প্ল্যাটফর্মও রয়েছে এতে। Nodriza (mothership) নামে পরিচিত এই জাহাজগুলিকে নিয়ে তারা অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে এগিয়েছে। এখন তারা তৈরি করছে এর চতুর্থ জেনারেশনের ডিজাইন। কলম্বিয়ার অভ্যন্তরের গৃহযুদ্ধে সরকারী বাহিনীর সাফল্যের পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে এই Nodriza-এর। এই জাহাজগুলি কোন অপারেশনে গিয়ে বেশ কয়েকদিন দুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করতে পারে। এর সাথে ছোট দ্রুতগামী এসল্ট বোটের একটি বা দুইটি স্কোয়াড থাকে (৪টি বা ৮টি বোট), যেগুলিকে বিভিন্ন অপারেশনে সাপোর্ট দেয় এই জাহাজ। জাহাজের ভেতরে এই এসল্ট বোটের ক্রু-দের থাকার জায়গা থাকে, সাথে বোট চালানোর জ্বালানিও থাকে; অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ফ্লোটিং বেইস। কোন সৈন্য আহত হলে তাকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে দ্রুত সড়িয়ে নেবার ব্যবস্থাও থাকছে। এই জাহাজ এবং এর সাথের এসল্ট বোটগুলি গুরুত্বপূর্ণ নদীপথের আশপাশের এবং উপকূলীয় ভূমিতে কর্তৃত্ব রাখতে অতুলনীয়। তবে এই জাহাজ সবধরনের নদী-কেন্দ্রিক মিশনের জন্যে উপযুক্ত নয়। নদীর পাড় যদি অনেক শক্তিশালী স্থলবাহিনীর হাতে থাকে, তাহলে বড় ধরনের উভচর অভিযান চালাতে যে সংখ্যক সৈন্য পরিবহণ করতে হবে, সেটার জন্যে আমাদের কলম্বিয়া থেকে বের হতে হবে।
 |
| ১৯৩৮ সালে তৈরি ব্রাজিলের নৌবাহিনীর রিভার মনিটর Parnaiba এখনো চলছে। সাম্প্রতিককালে এতে হেলিডেক যোগ করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তবে আসল ব্যাপার হলো একে এখনো প্রতিস্থাপন করা যায়নি। |
ব্রাজিলের নদী পাহাড়া
ব্রাজিলের নৌবাহিনী নদীপথে ব্যবহার করছে বেশ কয়েকটি পরিবহণ জাহাজ, যেগুলি বড় সংখ্যক সৈন্য পরিবহণে সক্ষম। আমাজনের দুর্গম অঞ্চলে সৈন্য নেবার পদ্ধতি এটাই। একই সাথে তাদের রয়েছে কয়েকটি রিভার হসপিটাল শিপ। আরও রয়েছে বড় বড় কিছু amphibious warfare ship, যেগুলি আমাজন নদীতে উভচর অপারেশন চালাতে পারে। আমাজন নদী থেকে কিছু দূরে ব্রাজিলের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পারানা নদীতে টহল দেয় ১৯৩৮ সালে তৈরি monitor ship ‘Parnaiba’, যা পৃথিবীর সবচাইতে পুরোনো যুদ্ধজাহাজগুলির মধ্যে একটি। ৫৫মিটার এবং ৭২০টনের এই জাহাজে ৭৬মিমি, ৪০মিমি এবং ২০মিমি কামান বহণ করার পাশাপাশি একটা হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। ৫.২ফুট ড্রাফটের এই জাহাজটি বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের সাথে ব্রাজিলের নদী-কেন্দ্রিক সীমানা পাহাড়া দেয়। ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত পারানা নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে ব্রাজিলের জাহাজগুলিকে সমুদ্রে যেতে হলে প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার অনুমতি লাগে। এই নদীকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ আমেরিকার সবচাইতে ধ্বংসাত্মক ‘প্যারাগুয়ে যুদ্ধ’ (১৮৬৪-১৮৭০) হয়েছিল। যাই হোক, এতো বছরে ব্রাজিল কিন্তু তাদের ওই পুরোনো মনিটর জাহাজটিকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেনি; শুধু আরও উন্নত করেছে। নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন ডিজাইন নিয়ে এগুনোর সেই চেষ্টাটা দেখার জন্যে আমাদের যেতে হবে অন্য মহাদেশে; আরেক নদীতে; ইউরোপের রোমানিয়াতে; দানিয়ুব নদীতে।
 |
| শক্তির দিক বিচারে রোমানিয়ার নৌবাহিনীর রিভার মনিটরগুলি পৃথিবী-সেরা। দানিয়ুব নদী পাহাড়ায় এরাই সেরা। |
দানিয়ুবের দানব
রোমানিয়ার দক্ষিণ সীমানা থেকে এর পূর্বাঞ্চল দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে দানিয়ুব। রোমানিয়া অনেকদিন যাবতই river monitor তৈরি করছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে ‘Smardan’-class-এর (৫১মিটার, ৩৭০টন। ৪ফুট১১ইঞ্চি ড্রাফট) পাঁচটি এবং ১৯৯০-এর দশকে রোমানিয়া ‘Mihail Kogălniceanu’-ক্লাসের (৫২মিটার, ৫২২টন, ৫ফুট৩ইঞ্চি ড্রাফট) তিনটি মনিটর যুদ্ধজাহাজ তৈরি করে। শেষোক্ত জাহাজগুলি দুইটি ১০০মিমি কামান এবং ৮০টি ১২২মিমি রকেট ছাড়াও ৩০মিমি এবং ১৪.৫মিমি কামানে সজ্জিত। একেবারে ভাসমান আর্টিলারি যাকে বলে আরকি। ‘Smardan’-class-এর জাহাজগুলিও একটি ১০০মিমি কামান, ৮০টি ১২২মিমি রকেট সহ ২৩মিমি ও ১৪.৫মিমি কামানে সজ্জিত। দুই ক্লাসের জাহজই আবার কাঁধে বহণযোগ্য বিমান ধ্বংসী মিসাইল নেয়। এই জাহাজগুলির ড্রাফট মাত্র ৫ ফুটের মতো; অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ে অনেক অগভীর পানিতে আবির্ভূত হয়ে এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নদীপথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ব্যাপক আকারে উভচর অভিযানের মাধ্যমে নদীর অপর পাড়ে ব্রিজহেড গড়ার অপারেশনে এসব জাহাজ বিশেষ উপযোগী। এই জাহাজগুলি উভচর অভিযানের সময়ে শত্রুপক্ষের ফর্মেশনের উপরে রকেট এবং কামানের মাধ্যমে ইনিডিরেক্ট ফায়ারিং যেমন করতে পারবে, তেমনি নদীতীরে শত্রুদের স্থির বা চলমান যেকোন লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি কামানের গোলাবর্ষণ (ডিরেক্ট ফায়ারিং) করতে পারবে। কলম্বিয়ার PAF যুদ্ধজাহাজগুলির ফায়ার সাপোর্ট যেখানে কম হয়ে হতে যেতে পারে, সেখানে রোমানিয়ার এই river monitor-গুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে। তবে PAF-এর মতো এই monitor-গুলি কোন রিভার এসল্ট বোটের গ্রুপকে সাপোর্ট দিতে পারে না। দ্রুতগামী জিআরপি এসল্ট বোট নিয়ে
শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের পোস্টে লিখেছি। এখানে সেই একই বোট নিয়ে আবার লিখছি না। তবে যদি দ্রুততার স্থানে বর্মাবৃত বোটের দরকার হয় রিভার এসল্ট অপারেশনে? এটা দরকার হতে পারে যখন শত্রুরা সংখ্যায় বেশি এবং যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রে সজ্জিত, যেমন হেভি মেশিন গান, মর্টার, রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড ইত্যাদি। এধরনের পরিবহণ খুঁজতে হলে আমাদের আবার এশিয়াতে ফেরত আসতে হবে; ইন্দোচীনের মেকং নদীতে।
_in_Vietnam_c1968.jpg/500px-Armoured_Troop_Carrier_(ATC)_in_Vietnam_c1968.jpg) |
| ভিয়েতনামে মার্কিন নৌবাহিনী Armored Troop Carrier (ATC) তৈরি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকহারে তৈরি করা LCM-6 ল্যান্ডিং ক্রাফটকে ওয়ার্কশপে নিয়ে পরিবর্তনের
(conversion) মাধ্যমে। এর উপরের কভারটি দেওয়া হয়েছিল মর্টার রাউন্ড থেকে বাঁচার জন্যে, আর বডির উপরে লোহা দিয়ে স্ট্রাকচার বানানো হয়েছিল এন্টি-ট্যাঙ্ক রকেট থেকে বাঁচার জন্যে। |
মেকং নদীর বদ্বীপে এসল্ট ফোর্স
ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গুরুত্বপূর্ণ নদীপথগুলিকে সচল রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করে যে পুরো মেকং নদীর বদ্বীপ থেকে কমিউনিস্ট গেরিলাদের উতখাত করতে হবে। তারা পুরো উপকূলে নৌ-অবরোধ দেয়া ছাড়াও বদ্বীপ অঞ্চলে Mobile Riverine Force (MRF) নামে এক বাহিনী গঠন করে ১৯৬৭ সালে। MRF-এর নৌবাহিনীর অংশকে বলা হতো Task Force 117 (TF-117) এবং এতে ছিল চারটি River Assault Division, যার প্রতিটিতে ছিল ১৩টি করে Armored Troop Carrier (ATC), তিনটি করে monitor, একটি Command and Control Boat (CCB) এবং ৮টি করে Assault Support Patrol Boat (ASPB)। ATC, monitor এবং CCB – এই তিনটি জলযানই তৈরি করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত LCM-6 ল্যান্ডিং ক্রাফটকে ওয়ার্কশপে নিয়ে পরিবর্তনের (conversion) মাধ্যমে। ৫৬ফুট লম্বা এবং সাড়ে তিন ফুট ড্রাফটের ATC-গুলি মোটাগুলি ৪০ জনের মতো একটা প্লাটুন পরিবহণ করতো, এবং তাতে একইসাথে ২০মিমি কামান, দু’টা ১২.৭মিমি হেভি মেশিন গান এবং গ্রেনেড লঞ্চার থাকতো। “Tango” বোট নামে পরিচিত এই বোটের বডিতে আলগাভাবে রডের তৈরি স্ট্রাকচার লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেগুলি নদীর পাড় থেকে কেউ রিকোয়েললেস রাইফেল বা এন্টি-ট্যাঙ্ক রকেট ছুঁড়লে সেটা থেকে বোটকে বাঁচাতো। এর উপরে ত্রিকোণাকৃতির একপ্রকার ক্যানভাসের ঢাকনা দিয়ে দেওয়া হয়, যেটা বোটের উপরে ছুঁড়ে দেওয়া গ্রেনেডকে বোটের পাশে পানিতে ফেলে দিতে সাহায্য করতো। Monitor-গুলির ক্ষেত্রে অবশ্য ল্যান্ডিং ক্রাফটের সামনের র্যাম্প সড়িয়ে চোখা করে দেওয়া হয়। ATC-এর অস্ত্রের উপরে এই বোটগুলিতে থাকতো ৪০মিমি কামান এবং ৮১মিমি মর্টার। ৬০ ফুট লম্বা এই বোটগুলিকে “নদীর ব্যাটলশিপ” বলে ডাকতো অনেকেই। তবে রোমানিয়ার নৌবাহিনীর মনিটরগুলির কাছে এগুলি যে কিছুই না, সেটা বলাই বাহুল্য। কিছু মনিটর জাহাজকে মার্কিনরা Flame Thrower দিয়ে সজ্জিত করে, যেগুলিকে তারা সিগারেট লাইটারের ব্র্যান্ডের নামানুসারে “Zippo Boat” বলে ডাকতো! CCB-গুলি মনিটরের মতোই ছিল, শুধু ৮১মিমি মর্টারের স্থানে এতে থাকতো রেডিও এবং যোগাযোগ যন্ত্রপাতি। CCB এবং মনিটরে নৌচলাচলে সুবিধার জন্যে রাডার থাকতো। এই একই ল্যান্ডিং ক্রাফট থেকে ১০,০০০ গ্যালন জ্বালানি পরিবহণের জন্য রিফুয়েলার বোট, সার্জারির যন্ত্রপাতিসহ হসপিটাল বোট এমনকি আহতদের সড়ানোর জন্যে হেলিকপ্টার প্ল্যাটফর্ম বোটও (বোটের বেশিরভাগটাই হেলিপ্যাড থাকতো) তৈরি করা হয়েছিল। ASPB-গুলি ছিল ভিয়েতনামকে মাথায় রেখে ডিজাইন করা বোট। ৫০ ফুটের এই বোটগুলি শক্ত খোলে তৈরি ছিল বলে পানিতে মাইন বিস্ফোরণ সহ্য করতে পারতো বেশ। মাইন সুইপার হিসেবেও এই বোটগুলি ব্যবহার হতো। ৮২মিমি মর্টার, ২০মিমি কামান এবং মেশিন গান থাকতো এগুলিতে।
 |
| ভিয়েতনামের একটি Mobile
Riverine Base or MRB, যেখানে ঘাঁটিটি ছিল কনভার্ট করা ল্যান্ডিং শিপ, যা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তৈরি করা হয়েছিল। পাশের ছোট বোটগুলি হলো ATC, CCB এবং monitor, যেগুলি সবগুলিই কনভার্ট করা ল্যান্ডিং ক্রাফট। জাহাজের উপর থেকে হেলিকপ্টার অপারেট করতো।
|
এই বোটগুলি একটা ভাসমান ঘাঁটির (Mobile Riverine Base or MRB) সাথে যুক্ত থাকতো, যেখান থেকে তারা মিশন পরিচালনা করতো। এই ঘাঁটিগুলি প্রধান নদীর মুখে অবস্থান করতো; সেখান থেকে এসল্ট ফোর্স আক্রমণে যেত। সেই ঘাঁটির প্রধান জাহাজ ছিল দুইটি ব্যারাক শিপ, যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তৈরি ট্যাঙ্ক ল্যান্ডিং শিপ (Landing Ship Tank or LST) থেকে পরিবর্তন (conversion) করে তৈরি করা। এর সাথে থাকতো দুইখানা ফ্লোটিং ব্যারাক যেগুলি নিজে চলতে পারতো না, একটা রিপেয়ার শিপ (LST থেকে পরিবর্তন করে তৈরি) যা ছোট বোটগুলিকে মেরামতের কাজ করতো, একটা নেট লেয়িং শিপ (Net Laying Ship) যা জাল বিছিয়ে পানির নিচে দিয়ে ফ্রগম্যানদের আক্রমণ থেকে ঘাঁটিকে রক্ষা করতো, এবং দুইখানা টাগবোট, যা পানিতে কোনকিছু ঠেলাঠেলি বা টানাটানির কাজ করতো। পুরো ঘাঁটিটি জায়গা পরিবর্তন করতে পারতো; যখন যেখানে দরকার চলে যেত এবং মিশন শেষ করে আবার স্থান পরিবর্তন করতো। এখানে ঘাঁটির বড় জাহাজগুলির ড্রাফট ছিল ৮ফুট থেকে ১১ফুট, অর্থাৎ এই ঘাঁটি শুধু বড় নদীর মুখে অবস্থান করতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন নৌবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি করা অনেকগুলি জাহাজ ব্যবহার করেছে এই নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী তৈরি করতে। জাহাজ এবং ছোট বোটের এই বাহিনী ছিল নৌবাহিনীর অধীনে, কিন্তু এদের দ্বারা পরিবাহিত সেনারা ছিল মার্কিন সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের। মেকং নদীর বদ্বীপে এসল্ট অপারেশন চালানোর জন্যে TF-117-কে তৈরি করা হয়েছিল। তবে এই বাহিনী নদীতে পাহাড়ার কাজ করতো না; সেই কাজ করতো Task Force 116 (TF-116). এসল্ট ফোর্সের কাজ শুরুর আগেই এই TF-116 কাজ শুরু করে।
 |
| গ্লাস-ফাইবারে তৈরি ৩১ ফুট লম্বা Patrol Boat River (PBR) ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে সবচাইতে বেশি সংখ্যক তৈরি করা হয়েছিল। এগুলি সর্বক্ষণ মেকং নদীর বদ্বীপ পাহাড়া দিতো। আর মাত্র ৯ইঞ্চি গভীর পানিতে চলতে পারতো! |
মেকং রিভার প্যাট্রোল
TF-116 বা River Patrol Force কাজ করা শুরু করে ১৯৬৬ সাল থেকে। এর প্রধান বোট ছিল গ্লাস-ফাইবারে তৈরি ৩১ ফুট লম্বা Patrol Boat River (PBR). ওয়াটার জেটে চলা এই বোটগুলি মাত্র ৯ ইঞ্চি পানিতে চলতে সক্ষম ছিল! অস্ত্র হিসেবে এই বোটগুলি ১২.৭মিমি এবং ৭.৬২মিমি মেশিন গান এবং গ্রেনেড লঞ্চার ব্যবহার করতো। এসল্ট ফোর্সের বোটগুলি যেখানে ঘন্টায় ১২ থেকে ১৬ নটিক্যাল মাইলের বেশি গতিতে চলতে পারতো না, সেখানে এই ছোট্ট PBR বোটগুলি ২৫ থেকে ২৯ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে পারতো। ভিয়েতনামি গেরিলাদের ব্যবহার করা বোট এরা তাড়া করতো; তাদেরকে নদীর মাঝে ও পাড় ঘেঁষে ধাওয়া করতো; সারাদিন ধরে নদীতে টহল দিয়ে ছোট-বড় সকল নৌকায় অস্ত্র, সামরিক জনবল ও অন্যান্য সাপ্লাই-এর চালান ধরার জন্যে তল্লাশি করতো। অত্যন্ত অগভীর নদী-নালাও এদের প্যাট্রোল থেকে রক্ষা পেত না। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ২৫০টি এরকম বোট তৈরি করা হয়েছিল। মোট পাঁচটি River Division পাঁচটি স্থান (নদীর তীর বা ভাসমান কোন ঘাঁটি) থেকে অপারেট করতো, যেগুলির একেকটিতে দুইটি করে সেকশন থাকতো। একেকটি সেকশনে ১০টি করে এভাবে ২০টি বোট থাকতো প্রতি ডিভিশনে। এগুলিকে সাপোর্ট দেবার জন্যে ৫টি জাহাজ মোটামুটি সবসময়েই প্রস্তুত ছিল। এই জাহাজগুলি ছিল সেই TF-117-এর ঘাঁটির মতোই, অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি করা ট্যাঙ্ক ল্যান্ডিং শিপ, যেগুলিকে পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জাহাজগুলির ডেকের উপরে হেলিপ্যাড বসানো হয়েছিল যেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে সৈন্য পাঠানো হতো।
 |
| মার্কিন নৌবাহিনী তাদের বেশকিছু ল্যান্ডিং শিপকে রকেট লঞ্চার দিয়ে সাজিয়ে
ফায়ার সাপোর্ট শিপ বানিয়ে ফেলে। এই জাহাজগুলি উভচর অভিযানের সময়ে বেশ
ব্যাপক পরিমাণে ধ্বংসজজ্ঞ চালাতে সক্ষম ছিল। |
মেকং-এর মাইন সুইপার এবং ফায়ার সাপোর্ট শিপ
TF-116 এবং TF-117-এর যে ফোর্সগুলির কথা বলা হয়েছে, তা ছাড়াও মেকং বদ্বীপ অঞ্চলে স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা অপারেট করতো। এরা আলাদা ঘাঁটিতে থাকতো এবং বিভিন্ন ধরনের নৌযান ছাড়াও হেলিকপ্টার ব্যবহার করতো। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী তৈরিতে, যেটা মেকং বদ্বীপ অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। TF-116-এর অধীনে ছিল Mine Division 112 (Mine Squadron 11, Detachment Alpha), যার কাজ ছিল প্রধান সমুদ্রবন্দর সায়গনের সাথে সমুদ্রের সংযোগ করা প্রধান নদীপথকে মাইন থেকে মুক্ত রাখা। ৫৭ ফুট লম্বা কাঠের তৈরি Mine Sweeping Boat (MSB)-গুলি দেখতে পল্কা হলেও এগুলির কাজ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নদীতে মাইনসুইপিং করে এরা সমুদ্রবন্দরকে সচল রেখেছিল। মার্কিনীরা অনেক ধরনের মাইনসুইপারের সাথে এই MSB-গুলি তৈরি করেছিল ১৯৫০-এর দশকে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে।
রিভার এসল্ট ফোর্সের জন্যে ফায়ার সাপোর্ট দিতে গিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনী এক সমস্যায় পড়ে। মেকং-এর জংলা যায়গার মাটিতে আর্টিলারি ফায়ার করার পরে নরম মাটিতে ডুবেই যেত। তাই তারা কিছু পন্টুন ডিজাইন করে, যেগুলি টাগবোট দিয়ে টেনে নিয়ে বিভিন্ন সুবিধাজনক যায়গায় নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে ইনডিরেক্ট ফায়ার সাপোর্ট দিত। তবে এই বাইরেও উপকূলের কাছাকাছি ফায়ার সাপোর্ট দিতে তাদের ছিল ফায়ার সাপোর্ট শিপ।
ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর সবচাইতে আলাদা রকম ইউনিটগুলির অন্যতম ছিল Inshore Fire Support Division 93 (IFSDIV93), যেটার দায়িত্ব ছিল উভচর অভিযানের সময় স্থলভাগের উপরে গোলাবর্ষণ। এই ইউনিটের ফ্ল্যাগশিপ ছিল USS Carronade, যেটা কিনা ১৯৫০-এর দশকে কোরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ডিজাইন করা হয়েছিল এই কাজের জন্যেই। ৭৫ মিটার লম্বা এই জাহাজ প্রতি মিনিটে ২৪০টা আর্টিলারি রকেট নিক্ষেপে সক্ষম ছিল। এর সাথে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি ৬৩ মিটার লম্বা তিনটি Landing Ship Medium (Rocket) বা LSM(R); এগুলিও সমান সংখ্যক রকেট নিক্ষেপ করতে পারতো। চারটি জাহাজেই রকেটের সাথে সাথে একটি করে ৫ ইঞ্চি কামান ছিল। LSM(R)-গুলি কোরিয়ার যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এবং যুদ্ধশেষে ডিকমিশন করে ফেলা হয়। ভিয়েতনামে এই জাহাজগুলি আবারও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার সাথে সাথেই ডিকমিশন করে ফেলা হয়।
 |
| আমেরিকান
গৃহযুদ্ধের সময়ে তৈরি রিভার মনিটর। মার্কিনীরা রিভারাইন ফোর্স গঠন করেছে
বেশ কয়েকবার, কিন্তু কখনোই সেটা রেখে দেয়নি; প্রতিবারই ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা
দরকার হাজির হলেই কেবল রিভারাইন ফোর্স গঠন করেছে।
|
রিভারাইন ফোর্সের স্থায়িত্ব – মার্কিনী বনাম কলম্বিয়া/রোমানিয়া/সার্বিয়া
উপরে বর্ণিত মার্কিনীদের বেশিরভাগ বোটের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে তারা সেগুলিকে কাজ শেষ হয়ে গেলেই অবসরে পাঠিয়ে দিয়েছে বা বিক্রি করে দিয়েছে। মার্কিনীরা কখনোই সবসময়ের জন্যে নদী-কেন্দ্রিক বাহিনী ধরে রাখতে চায়নি। ১৮৩৫ থেকে ১৮৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতে আদিবাসীদের সাথে সংঘটিত Second Seminole War-এ আমেরিকা প্রথম রিভার ফোর্স তৈরি করে। যুদ্ধ শেষে সেটা তারা রাখেনি। এরপরে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালের আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়েও রিভার ফোর্স তৈরি করা হয়; সেটাও যুদ্ধ শেষে রাখা হয়নি। তাদের এই চিন্তাটা কলম্বিয়া বা রোমানিয়ার বাহিনী থেকে পুরোপুরি আলাদা। আমরা এখানে সার্বিয়ার কথাও আনতে পারি। দানিয়ুব নদী রোমানিয়া থেকে সার্বিয়ায় ঢুকে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের উপর দিয়ে গিয়ে হাঙ্গেরীতে ঢুকেছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই দানিয়ুব এবং সাভা নদী রক্ষায় নৌবাহিনী নিয়োজিত করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সার্বিয়ার বিদ্রোহীরা জার্মান-অধিকৃত সার্বিয়াতে দানিয়ুবের নদীপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। যুদ্ধের পর থেকে যুগোস্লাভিয়া এবং পরে সার্বিয়ানরা প্যাট্রোল বোট, এসল্ট ল্যান্ডিং ক্রাফট এবং মাইনসুইপার তৈরিতে বেশ গুরুত্ব দিতে থাকে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে তারা প্রতিবেশী দেশ হাঙ্গেরীতে তাদের তৈরি ৩.৫ ফুট ড্রাফটের Nestin-class রিভার মাইনসুইপার বিক্রিও করে। নদীর মাইনসুইপারের ব্যাপারটা সার্বিয়ানদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে নদীপথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীরা মাইনসুইপার ব্যবহার করেছিল একই গুরুত্বপূর্ণ কাজে; কিন্তু তারা সার্বদের মতো এই চিন্তাটাকে স্থায়িত্ব দেয়নি। ‘দরকার হলে তৈরি করে নেব’ –এই ধরনের একটা প্রবণতা তাদের মাঝে বিরাজ করেছে; আজও করছে। ২০০৫ সালের দিকে এসে নদী-কেন্দ্রিক এই চিন্তাটা তাদেরকে আবারও ধরে বসেছে; অর্থাৎ তাদের আবারো দরকার পড়েছে।
 |
| ২০০৩ সালে ইরাক দখলে পর মার্কিনীরা আবারও রিভারাইন ফোর্সের গুরুত্ব বুঝতে
শুরু করেছে। এবার তারা কোস্টাল এবং রিভারাইন একত্রে ডেভেলপ করছে। এর জন্যে
তাদের রয়েছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। |
বাগদাদ থেকে ঢাকা……
২০০৩ সালে ইরাক দখল করে নেবার পরে ইরাকে মার্কিন বাহিনী বুঝতে শেখে যে তাদের জন্যে ইউফ্রেটিস নদী নিয়ন্ত্রণের একটা বাহিনী দরকার। বেশ তাড়াহুড়া করেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের রিভারাইন ফোর্সের আদলে তারা আবারও সেই বাহিনী গঠন করে। Riverine Squadron 1 (RIVRON-1) নামের প্রথম ইউনিটটিকে ২০০৭ সালের মার্চে ইরাকের হাদিথা বাঁধ রক্ষার্থে পাঠানো হয়। ২০১২ সালের জুনে মার্কিন ম্যারিন কোরের Marine Expeditionary Security Group (MESG)-2-এর সাথে মিলে গিয়ে Coastal Riverine Force (CORIVFOR) তৈরি করা হয়। এর দায়িত্ব বর্তায় নদী এবং সমুদ্রবন্দর, উপকূলীয় স্থাপনা এবং মার্কিনীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নদী ও উপকূলীয় নৌপথের নিরাপত্তা দেওয়া। অর্থাৎ একদিকে যেমন নৌবাহিনী ও ম্যারিন কোরের সমন্বয়ে এই ফোর্স তৈরি করা হলো, তেমনি উপকূলীয় এবং নদীর অপারেশনকে একত্রে হিসেব করা শুরু হলো। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জন্যে নদী-কেন্দ্রিক যুদ্ধ নতুন না হলেও আজকের এই সেনাদের জন্যে নতুন; তাদের শিখতে হচ্ছে সবকিছুই। ইরাকে মোতায়েনের মাধ্যমে প্রতি নিয়তই তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে। ভিয়েতনামের মতোই এই ফোর্সের মুখরোচক নাম হয় “Brown Water Navy”.
এসময়েই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এই বাহিনীর স্থায়িত্ব নিয়ে। তাদের সামরিক চিন্তাবিদদের মাঝে যে প্রশ্নটি আসে তা হলো – আমরা কি এই বাহিনীকে শুধু ইরাকের জন্যেই তৈরি করছি, নাকি বাকি বিশ্বে ব্যবহার করার কথা মাথায় রেখে একে সেভাবেই ডিজাইন করবো? মার্কিনীরা দ্বিতীয় অপশনটাকেই বেছে নিয়েছে। ২০০৬ সালের মার্চে তৈরি করা এক রিপোর্টে রিভার ফোর্স কেমন হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বের ৩৮টি দেশের একটি লিস্ট তৈরি করা হয়, যেসব দেশের নদী এবং ততসংলগ্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে তাদের রিভারাইন ফোর্স কতটুকু প্রস্তুত, সেটার উত্তর খোঁজা হয়। লিস্টে যেসব দেশের নদীপথ বেশি লম্বা এবং যেসব দেশের বদ্বীপ অঞ্চল বেশি বড়, অর্থাৎ যেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বড় ফোর্স লাগতে পারে, সেগুলিকে আলাদাভাবে হাইলাইট করা হয় এই বলে যে সেগুলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের নেই এবং ভবিষ্যতেও সেইসব দেশের সরকার ও মানুষের সাহায্য ব্যতীত ওইসব নদী-অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। “গ্যাপ কান্ট্রি” বলে পরিচিত এই দেশগুলিতে ভবিষ্যত অপারেশনের কথা মাথায় রেখেই তারা তাদের হিসেব কষে। নদীপথের মোট দৈর্ঘ্য বিবেচনায় প্রথম সাড়ির ২২টি দেশের মাঝে বাংলাদেশের নাম রয়েছে প্রথম দশের ভেতরে। আর আরেকটি লিস্ট করা হয়েছে বদ্বীপের আকার (বর্গ কিঃমিঃ) হিসেবে, যেখানে রয়েছে মাত্র ১০টি দেশের নাম। এই লিস্টে বাংলাদেশের নাম ‘এক’ নম্বরে! আমাদের বদ্বীপ এলাকাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা যত উদাসীনই হই না কেন, দুনিয়ার উল্টোপাশে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বেশ চিন্তিত। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি অনুসারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স Special Wardare Diving Slvage (SWADS) গড়তে সহায়তা করে। বাংলাদেশের নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডকে তারা বেশ নিয়মিতই Metal Shark 38 Defiant, SafeBoats 25ft Defender আর Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) সিরিজের ছোট দ্রুতগামী বোট দিয়ে যাচ্ছে, আবার একই সাথে নিয়মিত যৌথ মহড়াও চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজির সাথে সমন্বয় করে এগুনোর ফলে আমাদের স্বার্থ যতটা না রক্ষিত হচ্ছে, তার চাইতে বেশি লাভ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের। বাংলাদেশের বদ্বীপের কতটুকু যে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না, সেটা বরং আজ চিন্তা করার সময় এসেছে। এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
 |
| বাংলাদেশের নদীগুলি দেশের মাঝ দিয়ে ধমনীর মতো প্রবাহিত এবং একইসাথে দেশের
স্থলভাগকে সুঁই-সূতা দিতে সেলাই করে রেখেছে। এদেশে রিভারাইন ফোর্স থাকাটা
একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হবার কথা ছিল; কিন্তু তা হয়নি। আমাদের চিন্তা ভুল
পথে প্রবাহিত হওয়াটাই এর জন্যে দায়ী। |
যমুনা নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং এর নিরাপত্তা
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী আর খুলনা অঞ্চলের ম্যারিটাইম গুরুত্ব মোটামুটি অনেকেই বোঝেন। তবে এর সাথে এই অঞ্চলগুলির নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা ভাবেন না। আর এই অঞ্চলগুলির বাইরের অঞ্চলগুলির নৌ-নিরাপত্তার কোন অস্তিত্বই নেই তাদের কাছে। এই দেশের অভ্যন্তরে ৯০% জ্বালানি তেল পরিবাহিত হয় নৌপথে। উজানে বেশিরভাগ নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীতে নাব্যতার যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার মাঝেও নদীপথের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে কমেনি। বরং এখন অনেকেই নদীপথের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকায় নতুন কর্মপদ্ধতি দেখতে চাইছেন। নদী ড্রেজিং-এর মাঝেই সমাধান যে নিহিত, সেটা আজ অনেকেই বুঝতে পারছেন। বাংলাদেশের নদীগুলির প্রকৃত গুরুত্ব খুঁজতে তাকাতে হবে দেশের মধ্যে ধমনীর মতো করে প্রবাহিত পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দিকে। যমুনা দিয়েই শুরু করা যাক।
উত্তরাঞ্চলে দেশের বিশাল শস্যক্ষেতে রাসায়নিক সারের সাপ্লাই দিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হচ্ছে বাঘাবাড়ি ঘাট এবং তার সাথে সেকেন্ডারি গুরুত্বে রয়েছে নগরবাড়ি ঘাট। উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্যে জ্বালানি তেলের সরবরাহও বাঘাবাড়ি দিয়েই হয়। শুষ্ক মৌশুমে বাঘাবাড়ি পর্যন্ত নাব্যতা রক্ষা বর্তমানে একটা বড় সমস্যা। সেখান থেকে উত্তরে নাব্যতা আরও অনেক খারাপ। গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রাম অঞ্চলে যমুনা নদীতে একসময় তেলের ডিপো ছিল, যা এখন নাব্যতার অভাবে অকার্যকর। তেলের সাপ্লাই নিশ্চিত না হওয়ায় উত্তরাঞ্চলে তেলের উপরে নির্ভর করে বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। জামালপুরের বাহাদুরাবাদ থেকে যমুনা পাড় হয়ে গাইবান্ধার ফুলছড়িঘাট ও বালাসিঘাট পর্যন্ত রেলওয়ের ফেরি ছিল (এখনও আছে), যা এখন নাব্যতার অভাবে কাজ করছে না। উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত নদীবন্দর কুড়িগ্রামের চিলমারী এবং বগুড়ার সারিয়াকান্দিরও শুষ্ক মৌশুমে একই অবস্থা হয়; তবে বর্ষায় এই বন্দরগুলিতে পানি থাকে। যমুনার পূর্বপাড়েও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গুঠাইল বাজার। এই বন্দরগুলি কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত। জামালপুরের সরিষাবাড়ির জগন্নাথগঞ্জে রেলওয়ের ফেরিঘাট রয়েছে, যা যমুনা সার কারখানার সাথে যুক্ত, কিন্তু নাব্যতার কারণে এটা এখন অকার্যকর। তিস্তা নদীর নাব্যতার অবস্থাও যা-তা; তাই রংপুরকে নদীপথে দেশের বাকি অঞ্চলের সাথে যুক্ত করা যাচ্ছে না। দেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করার জন্যে যমুনা নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। ব্যাপক খননের মাধ্যমে যমুনা নদীকে অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি ব্যবহার করতে গেলে সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নটাও এসে যাবে। নদীপথ, নদীবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (যেমন যমুনা নদীতে বর্তমান বঙ্গবন্ধু সেতু এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য সেতু) পাহাড়া দিতে রিভার প্যাট্রোল বা নৌটহলের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীতে কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনী বর্তমানে যেভাবে টহল দিচ্ছে সেভাবে যমুনাতেও টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। কুড়িগ্রামের পূর্বে যমুনাতে সীমানা টহলও এই ফোর্সের কাজ হওয়া উচিত। আলাদা ম্যারিটাইম জোন গঠন করতে হবে এই টহলের জন্যে। বর্তমানে কোস্ট গার্ড এই দায়িত্ব পালন করছে বলে তারাই এই কাজের জন্যে সবচাইতে উপযুক্ত বলে মনে হয়। Harbour Patrol Boat (HPB), High-Speed Patrol Boat (HSPB) ছাড়াও একেবারে অগভীর পানিতে চলার জন্যে উপযোগী বোট এই নদীপথ, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং নদীবন্দরগুলির আশেপাশে টহলে দরকার হবে। বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডগুলি এধরনের বোট এখন তৈরি করছে।
রিভারাইন ফোর্স (যমুনা)
তবে যমুনাতে টহলই সব নয়। এই নদী দেশের পশ্চিমাঞ্চলের সাথে মধ্যাঞ্চলের সেলাই-সদৃশ। এই সেলাইকে তখনই সেলাই বলা যাবে যখন যে কোন স্থান দিয়ে সামরিক বাহিনীর নদী পারাপারের সুবন্দোবস্ত থাকবে। এর জন্যে দরকার হবে রিভার এসল্ট ফোর্স। যেকোন সময়ে নদী পারাপার নিশ্চিত করা এবং নদীর দুই পাড় নিরাপদ রাখাই হবে এই ফোর্সের প্রধান কাজ এবং এগুলি হবে মূলত বিভিন্ন ল্যান্ডিং ক্রাফট, যেমন LCT, LCU, LCM, LCVP ইত্যাদি, যা নৌবাহিনীই সবচাইতে ভালো হ্যান্ডেল করতে পারবে। এগুলির সংখ্যা এবং আকার হওয়া উচিত কি পরিমাণ সৈন্য এবং রসদ একবারে পরিবহণ করা হবে, সেটার উপরে। এই এসল্ট ফোর্সের সেনারা আসা উচিত সেনাবাহিনী থেকে, যেটা নদীর দুই পাড়ের সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করা সহজ করবে। তবে শুধুমাত্র যমুনা সেতু রক্ষার জন্যে গঠিত ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড যমুনা নদীর পুরো দৈর্ঘ্যের জন্যে যথেষ্ট না-ও হতে পারে। যমুনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে, যেগুলির নিরাপত্তা দিতে গিয়ে এই ফোর্সের একটি থেকে তিনটি সিকিউরিটি ব্যাটালিয়ন লেগে যেতে পারে। এদের প্রধান কাজ হবে হার্বার ডিফেন্স বা নদীবন্দর রক্ষা। এক্ষেত্রে বন্দরের ভিতরে এবং বাইরে নিরাপত্তা দেওয়াই হবে এই অংশের কাজ। সাথে ৯৮ কম্পোজিটের মতো সেতু রক্ষাও হবে এর দায়িত্ব। এসল্ট ফোর্স হওয়া উচিত আলাদা এবং এর আদর্শ আকৃতি হতে পারে একটা মোবাইল ব্রিগেড।
একই সাথে উভচর অপারেশনে সাহায্য করার জন্যে স্পেশাল ফোর্সের বোটেরও (জিআরপি-তে তৈরি) একটা গ্রুপ দরকার হবে, যে ধরনের বোটের কথা শ্রীলঙ্কা নিয়ে পোস্টে লিখেছি। আর এই রিভার এসল্ট ফোর্সের ফায়ার সাপোর্ট আসবে কিছু ফায়ার সাপোর্ট জাহাজ থেকে, যেগুলি নৌবাহিনীর কাছে থাকাটাই সমীচিন হবে। আমরা এর জন্যে তাকাতে পারি রোমানিয়ার রিভার মনিটরগুলির দিকে। আবার ভিয়েতনামে মার্কিনীদের ব্যবহৃত রকেট ফায়ার সাপোর্ট শিপও আমরা দেখতে পারি, যা কিনা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে ডিজাইন করা, কারণ ল্যান্ডিং ক্রাফট ডিজাইন এমনকি বাণিজ্যিক পরিবহণ জাহাজের নকশা পরিবর্তন করেই এটা বানানো সম্ভব। আমাদের দেশের শিপইয়ার্ডগুলি যেহেতু ল্যান্ডিং ক্রাফট তৈরি করে, তাই এটা খুব একটা কঠিন কাজ হবার কথা নয়। ৩ থেকে ৪টা রিভার মনিটর নদীর প্রায় পুরো দৈর্ঘ্যেই নিরাপত্তা দিতে পারবে বলে আশা রাখি। তবে আমাদের এই মনিটরে আমি এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল রাখার পক্ষপাতি, যেহেতু সরাসরি স্থলভাগের শত্রুর সাথে সংঘর্ষের একটা সম্ভাবনা এখানে থাকবে। আর এগুলিকে এসল্ট রিভার ক্রসিং অপারেশনে ইনডিরেক্ট ফায়ার সাপোর্টের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে একই সংখ্যক রকেট ফায়ার সাপোর্ট শিপ।
রিভারাইন ফোর্সের আরেকটা অংশ গুরুত্বপূর্ণ, যেটা উপরে সার্বিয়ার দানিয়ুব রক্ষার কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করেছি, তা হলো মাইনসুইপার। যমুনার প্রতিটি নদীবন্দর মাইনিং করা সম্ভব, কাজেই এগুলিকে মাইন থেকে রক্ষা করাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নদীর অগভীর পানিতে অপারেট করতে সক্ষম মাইনসুইপার এই ফোর্সের অংশ হওয়া উচিত। মাইন পরিষ্কার না করতে পারলে নদীপথ তো অনিরাপদ হতেই পারে, সাথে এসল্ট ফোর্সও বিপদে পড়তে পারে। এই মাইনসুইপারগুলি শান্তিকালীন সময়ে টহল এবং সার্ভের কাজে লাগানো যেতে পারে। ৪ থেকে ৬টি মাইনসুইপার যমুনার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। যমুনার জন্যে উপসংহারে বলা যায় যে, “রিভারাইন ফোর্স (যমুনা)”-তে থাকা উচিত –
- রিভার প্যাট্রোল ফোর্স (HSB, HSPB, other boats, logistical boats, shore bases)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (রিভার এলিমেন্ট) (LCT, LCU, LCM, LCVP)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (গ্রাউন্ড এলিমেন্ট) (1 independent army brigade)
- ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ (3-4 river monitors, 3-4 rocket fire support ships)
- স্পেশাল ফোর্স বোট গ্রুপ (Special ops forces and GRP boats)
- মাইনসুইপার ফোর্স (4-6 river minesweepers) এবং
- হার্বার ডিফেন্স (2-3 security battalions)।
রিভারাইন ফোর্স (পদ্মা-মহানন্দা)
যমুনা নদীর এই মডেল আমরা মোটামুটিভাবে কপি করতে পারি পদ্মা, মহানন্দা এবং সুরমা নদীর ক্ষেত্রে। যমুনার মতোই এই নদীগুলিতেও খনন করাটা জরুরি। পদ্মা নদীর পশ্চিমাংশের (পাবনা থেকে পশ্চিমে) কথাই এখানে প্রধানত উল্লেখ করতে চাই। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রবন্দরের সাথে সেলাই করে যুক্ত করেছে এই নদী। পাকশীতে দুইটি সেতু (হার্ডিঞ্জ এবং লালন শাহ সেতু) রয়েছে এই নদীতে, যেগুলির নিরাপত্তা খুবই জরুরী। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট রয়েছে এই নদীতে। এর সাথে যোগ হচ্ছে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র এবং ভবিষ্যতের গঙ্গা ব্যারেজ। পরের দুইটি স্থাপনা তৈরি হলে নদীর গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। গঙ্গা ব্যারেজ হয়ে গেলে রাজশাহী এবং কুষ্টিয়াসহ বেশ কিছু শহর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে নদীপথে যুক্ত হবে। পদ্মা নদীতে সীমানা টহলের ব্যাপারটাও থাকছে। আর মহানন্দা নদী পদ্মার সাথেই যুক্ত, কাজেই একে আলাদা করে দেখার সুযোগ কম। পদ্মার কথা চিন্তা করে “রিভারাইন ফোর্স (পদ্মা-মহানন্দা)”-তে আমরা যমুনার কপি হিসেবে দেখাতে পারি –
- রিভার প্যাট্রোল ফোর্স (HSB, HSPB, other boats, logistical boats, shore bases)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (রিভার এলিমেন্ট) (LCT, LCU, LCM, LCVP)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (গ্রাউন্ড এলিমেন্ট) (1 independent army brigade)
- ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ (3-4 river monitors, 3-4 rocket fire support ships)
- স্পেশাল ফোর্স বোট গ্রুপ (Special ops forces and GRP boats)
- মাইনসুইপার ফোর্স (4-6 river minesweepers) এবং
- হার্বার ডিফেন্স (1-2 security battalions)।
রিভারাইন ফোর্স (হাওড়)
অন্যদিকে সিলেটের সুরমা নদী এখনই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে খনন করা হলে এর গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ফসলের ক্ষেতে সেচের জন্যে জ্বালানি তেলের ডিপো রয়েছে, আবার সিলেট শহরের দক্ষিণেও রয়েছে রেলের সরবরাহের অধীনে জ্বালানি তেলের ডিপো, যেখানে বিমানের জ্বালানি রাখা হয়। এর পুরোটাই সুরমা নদী ব্যবহার করে করা যায়। এখন সুরমা নদী দিয়ে মূলত বালু, পাথর, কয়লা এবং ছাতকের সিমেন্ট কারখানার সিমেন্ট পরিবহণ হচ্ছে। ঠিকমতো ব্যবহার করা গেলে এই নদী বৃহত্তর সিলেট, তথা সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের পুরো হাওড় অঞ্চলের অর্থনৈতিক চাবি হতে পারে। তখন হাওড়ে একটা শক্তিশালী রিভা্রাইন ফোর্স দরকার হবে। এই নদী এবং হাওড় যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ মেঘনা নদীর সাথে যুক্ত, তাই এর অপারেটিং এরিয়াও বেশ বড় হবে – একেবারে নোয়াখালী থেকে সিলেট পর্যন্ত পুরো নদীপথ। চট্টগ্রাম-ঢাকা নৌপথ এটি। এর মাঝে চাঁদপুর, মেঘনাঘাট, ভৈরব, আখাউড়া, গজারিয়া-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে; রয়েছে মেঘনার উপরে এখন পর্যন্ত তৈরি করা চার-চারটি সেতু। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেটের সড়ক ও রেলপথ এই নদীর উপর দিয়ে গিয়েছে। আবার একইসাথে বেশ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফেরী এই নদীর এপাড়-ওপাড় করছে।
তবে হাওড় অঞ্চল হবার কারণে এখানে বড় জাহাজের সংখ্যা বাড়ানো কঠিন হবে, এবং অপেক্ষাকৃত কম ড্রাফটের বোট বেশি ব্যবহার করতে হবে। এখানে উত্তর-পূর্বের সীমানা পর্যন্ত সবক্ষেত্রে বড় নদী না থাকায় মনিটর বাদ দিয়ে, এবং এলাকা বিশাল থাকায় একটা অতিরিক্ত ব্রিগেডের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে লজিস্টিক সাপ্লাইয়ের জন্যে বেশি বোট লাগতে পারে, কারণ অনেক স্থানেই বর্ষাকালে সাপ্লাই পাঠানোর একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াবে নৌপথ। এগুলি শান্তিকালীন সময়ে সাধারণ পরিবহণের কাজ করতে পারে।
“রিভারাইন ফোর্স (হাওড়)”-এ থাকা উচিত –
- রিভার প্যাট্রোল ফোর্স (HSB, HSPB, other boats, logistical boats, shore bases)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (রিভার এলিমেন্ট) (LCT, LCU, LCM, LCVP)
- রিভার এসল্ট ফোর্স (গ্রাউন্ড এলিমেন্ট) (2 independent army brigades)
- ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ (6-8 rocket fire support ships)
- স্পেশাল ফোর্স বোট গ্রুপ (Special ops forces and GRP boats)
- মাইনসুইপার ফোর্স (6-8 river minesweepers)
- রিভার লজিস্টিক গ্রুপ (shallow-draft transport ships) এবং
- হার্বার ডিফেন্স (2-3 security battalions)।
রিভারাইন ফোর্স (ম্যানগ্রোভ)
এরপরে আসি খুলনা অঞ্চলের দিকে। এই লম্বা আলোচনার শুরুর দিকে কলম্বিয়ার রিভার ফোর্স নিয়ে কথা বলেছি। তাদের PAF জাহাজগুলিকে কেন্দ্র করে গঠিত রিভার এসল্ট ফোর্সগুলি জংলা যায়গায় বেশি কার্যকর, যেখানে বড় ধরনের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার সম্ভাবনা কম। ঠিক এই অবস্থাটাই বিরাজ করছে সুন্দরবনসহ বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে। এখানে সীমানা পাহাড়া দেওয়া ছাড়াও রয়েছে মংলা বন্দর এবং এর আশেপাশের স্থাপনাগুলিকে রক্ষার বিরাট দায়িত্ব। এখানে রিভারাইন ফোর্স গঠন করতে গেলে যমুনা-পদ্মা-সুরমার এসল্ট ফোর্সের স্থানে কলম্বিয়া-স্টাইলের এসল্ট ফোর্স বেশি কার্যকর হতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম ড্রাফটের বোটও এখানে বেশি দরকার হবে। ৩ থেকে ৪টি রিভার এসল্ট গ্রুপ এখানে তৈরি করা যেতে পারে, যেগুলির কেন্দ্রে থাকবে একটি করে কলম্বিয়া-স্টাইলের এসল্ট সাপোর্ট শিপ এবং সাথে একটি করে স্পেশাল ফোর্স-এর বোট গ্রুপ। আমরা আমাদের এলস্ট সাপোর্ট শিপে এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল রাখতে পারি নদীপথে কর্তৃত্ব রাখতে। কলম্বিয়ার PAF-এর মতো জাহাজে স্পেশাল ফোর্সের সদস্যদের থাকার জায়গা থাকলে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে অপারেট করতে অনেক সুবিধা হবে। আর যেহেতু এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দুর্গম, তাই এখানে ড্রোনসহ বিভিন্ন এয়ার এলিমেন্ট বেশি ব্যবহার করতে হতে পারে।
“রিভারাইন ফোর্স (ম্যানগ্রোভ)”-এ থাকা উচিত –
- রিভার প্যাট্রোল ফোর্স (HSB, HSPB, other boats, logistical boats, fixed & floating bases)
- ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ (3-4 assault support ships)
- স্পেশাল ফোর্স বোট গ্রুপ (3-4 Special ops groups with GRP boats)
- মাইনসুইপার ফোর্স (4-6 river minesweepers)
- ড্রোন এলিমেন্ট এবং
- হার্বার ডিফেন্স (1 security battalion)।
শেষবাক্য…
এছাড়াও বাংলাদেশে আরও বহু নদী এবং নদী-কেন্দ্রিক অঞ্চল আছে, যেগুলির গুরুত্বপূর্ণ অনেক। সেগুলিকে নিরাপত্তা দিতে হয়তো আলাদাভাবে রিভারাইন ফোর্স না-ও লাগতে পারে। কিছুদিন আগে
দুবলার চরের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম এক পোস্টে। রিভারাইন ফোর্স গঠনে সেই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের নিরাপত্তা সুসংগঠিত হতে পারে। আর ওই একই পোস্টে উল্লেখ করা নাফ নদী এখানে আলোচনায় আনছি না, কারণ সেটা উপকূলীয় নিরাপত্তার সাথে যুক্ত। সেটা নিয়েও লিখবো আশা রাখি।
বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে ধমনীর মতো প্রবাহিত হওয়া প্রধান নদীগুলি দেশের স্থলভাগকে সুঁই-সূতা দিয়ে যত্ন করে সেলাই করে রেখেছে। আমরা যদি এই সেলাই দুর্বল করে বা খুলে ফেলতে চাই, সেটা আমাদের নিজেদেরই বিপদ। দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা সেই সেলাইকে বরং সেলাই হিসেবে না দেখে ডিভাইডার হিসেবে দেখতে শিখেছি। এই চিন্তা পরিবর্তন না করতে পারলে রিভারাইন ফোর্সের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আর সেটা না করতে পারলে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে আমরা মূর্খই থেকে যাবো। বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত সৃষ্টার অদ্ভূত সৃষ্টি এই নদীগুলির ভূরাজনৈতিক গুরুত্বকে না বুঝতে পারলে আমাদের সামনে যে ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে, তা আমাদেরকে অবাক করবে বৈকি।






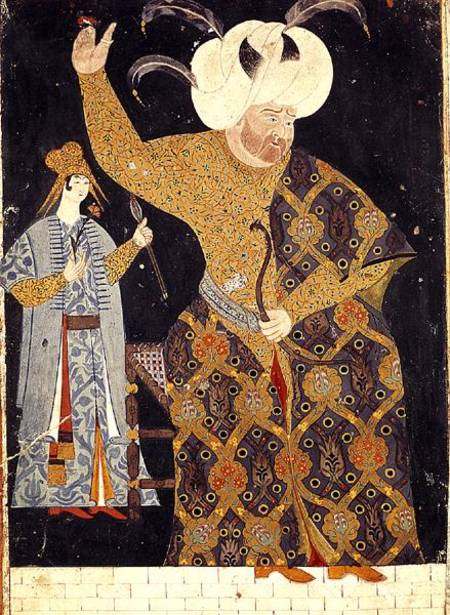








_in_Vietnam_c1968.jpg/500px-Armoured_Troop_Carrier_(ATC)_in_Vietnam_c1968.jpg)





