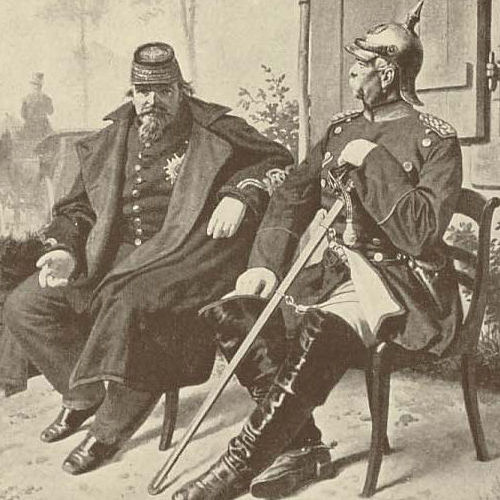০৪ জুলাই ২০১৬
গুলশান ৭৯ নম্বর রোডের ক্যাফেতে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। এর আগে যা যা নিয়ে লিখেছি, এই ঘটনা তারই চলমান প্রবাহ মাত্র। কিছুদিন আগেই আদর্শিক যুদ্ধের (Ideological Conflict) পুণরাবির্ভাব নিয়ে লিখেছিলাম, যেখানে বলেছিলাম যে পশ্চিমা আদর্শিক চিন্তাবিদ এবং ভূরাজনীতি বিশারদরা কিভাবে চিন্তা করছেন সামনের দিনগুলি নিয়ে। তারা সামনের দিনগুলিতে বিশ্বের Balance of Power-এ ব্যাপক পরিবর্তনের আশংকা করছেন বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তথা পশ্চিমা বিশ্বকে ‘উদ্ভট’ সব কৌশল অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছেন। ‘উদ্ভট’ বলছি আসলে সেগুলি উদ্ভট বলে নয়, বরং সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি উদ্ভট ঠেকবে সেজন্যে। যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে অন্য কথা বললেও দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু স্থানে সে আসলে স্থিতিশীলতা চায় না। স্থিতিশীলতা হচ্ছে একটা শক্তিশালী জাতি গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত। স্থিতিশীল জাতিই চিন্তা করে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের চিন্তার বিকাশের পথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সেই জাতি যদি অবাঞ্ছিত কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে চিন্তা করার সময়ও পাবে না এবং তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভিত্তিগুলিও হবে দুর্বল। এই প্রেক্ষাপটেই আজকে গুলশান ৭৯ নম্বর রোডের ঘটনার মূল্যায়ন করা চেষ্টা করবো।
গুলশান ৭৯ নম্বর – প্রাসঙ্গিক আলোচনা
গুলশানের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। তবে সবকিছু প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় সবকিছু নিয়ে কথা বলবো না। আর circumstantial evidence নিয়ে এখানে বেশি কথা বলতে চাই না, কারণ এগুলি manipulate করা সম্ভব। যেসব ব্যাপার ভূরাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে, শুধু সেসব ব্যাপার নিয়েই কথা বলবো।
প্রথমতঃ এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে এই অপারেশনে “বিদেশী” হওয়াটাই টার্গেট হবার মূল শর্ত ছিল। বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ হত্যা হওয়াটা সেটাই প্রমাণ করে। এখানে বিশেষ কোন শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা বা বিশ্বের সকল সমস্যার মূল বলে ধমকি দেবার মতো কোন রাজনৈতিক মেসেজ ছিল না। অর্থাৎ আক্রমণটা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে ছিল না।
দ্বিতীয়তঃ এক ঘন্টার মাঝে অপারেশন শেষ করে না ফেলে একটা জিম্মি সিচুয়েশনের অবতারণা করে সেটাকে ১০ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখার কি মানে দাঁড়ায়? কেউ কেউ কথা তুলবেন যে আইন-শৃংখলা বাহিনী ১০ ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু যে প্রশ্ন কেউ করবে না তা হলো, জিম্মিকারীদের কি খেয়ে কাজ ছিল না যে ১০ ঘন্টা বসে থাকবে? তারা যদি জানতোই যে তারা মারা পড়বে, তাহলে ১০ ঘন্টা ওখানে বসে ঘুমিয়ে তাদের লাভ কি ছিল? যদি সবাইকে মেরেই ফেলা হবে, তাহলে এত ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখে কিছু লোকের মুখে কথা তুলে দেয়া কেন? কিছু সমালোচক এখন কি করলে কি হতে পারতো, বা কখন কি করা উচিত ছিল, বা কোনটা করা ঠিক হয়নি, এগুলি নিয়ে কথা বলার সুযোগ তৈরি করা কেন? এক্ষেত্রে কথা বলার সুযোগ নিয়ে কে চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছে? জিম্মিকারীরা সেই চাপ সৃষ্টিকারীদের পক্ষেই কাজ করেছে।
তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ কোন পর্যটন কেন্দ্র নয়। এদেশে যে বিদেশীরা আসে, তার ৯০%-এরও বেশি আসে কাজ করতে। বিদেশীরা এদেশে আসেন বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে। কাজের ফাঁকে এরা দেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে আসে। যদি এদেশে বিদেশীদের উপরে হামলা হয়, তাহলে এদেশের পর্যটন শিল্পের কিছু হবে না, বরং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হত্যাকান্ডের শিকার জাপানিরা মেট্রো-রেল প্রজেক্টে কাজ করছিলেন আর ইটালিয়ানরা গার্মেন্টস ব্যবসায়ে ছিলেন; অর্থাৎ সকলেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এখানে এসেছিলেন। আরও নয়জন তাবেলা আর আরও সাতজন কুনিওকে হত্যা করা কেন? এই দু’টি দেশতো যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’ প্রথম সারির অংশগ্রহণকারী দেশ নয়। তাহলে এই দেশগুলিকে কেন টার্গেট করা? ইটালিয়ান এবং জাপানিরা তো অর্থনৈতিক কাজে এখানে আসে। এদের হত্যার মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য কি? কি হাসিল হবে এতে?
চতুর্থতঃ বাংলাদেশ তথা ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটা প্রয়াস মনে হতে পারে এটা। “আল্লাহু আকবার” কথাটাকে কলুষিত করে বেসামরিক বিদেশী হত্যা করে ইসলামকে বাজে ভাবে বাকি বিশ্বের সন্মুখে তুলে ধরার একটা ব্যর্থ প্রয়াস এটা। পশ্চিমা বিশ্বের মানুষই যেখানে প্রতিদিন ইসলামের মাঝে তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে ইসলামকে আলিঙ্গন করছে, সেখানে এধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো hawk-দের আকৃষ্ট করা ছাড়া আর কি অর্জন করা সম্ভব? ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা নয়, বরং পশ্চিমের hawk-দের মুখে কথা তুলে দেয়াটাই এর মূল উদ্দেশ্য। আর এর সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওইসব hawk-দের এজেন্টরা সক্রিয় হবে।
বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টির রেসিপি…
লম্বা সময়ে ওখানে বসে থাকার জন্যে পশ্চিমের এজেন্টরা এখন সুযোগ পাবে এই অপারেশনের সমস্যাগুলির কথা বলে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার। আর একইসাথে এদেশে অর্থনৈতিক কাজে আসা বিদেশীদের টার্গেট করে দেশের অর্থনীতির উপরে চাপ সৃষ্টি করে কিছু শর্ত চাপানোর কাজ চলবে। ঠিক যেমনটি ছয় মাস আগেই হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট এবং ফুটবল দলের ট্যুর নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি করে। এবং বিমানে পণ্য রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিশেষ শর্তগুলি চাপানোর কাজ না হবে, ততক্ষণ চাপ অব্যাহত থাকবে।
এখানে প্রকৃতপক্ষে রেস্টুরেন্টের মানুষগুলিকে জিম্মি করা হয়নি, বরং পশ্চিমের হাতে বাংলাদেশকে জিম্মি করার পথ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমারা বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, নিরাপত্তা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো আদর্শিক, যেটা বাস্তবায়নের জন্যেই বরং এই চাপ সৃষ্টি করা।
যাদের নাম দিয়ে এসব কর্মকান্ড চালানো হচ্ছে তারা যে প্রকৃতপক্ষে অন্য কারো সৃষ্টি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো এদের পক্ষে বর্তমান বিশ্বের কোন সমস্যার সমাধানই দেয়া সম্ভব নয়। ইসলাম কি করে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাখে, তা তাদের জানা নেই। তাদেরকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার কি করে সমাধান করবেন? সবার জন্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন কি করে? অথবা মার্কিন ডলার বা বিশ্ব ব্যাংককে কি করে মোকাবিলা করবেন? আন্তর্জাতিক আইন বা সমুদ্র আইন বা আকাশপথ ব্যবহারের আইনের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেবেন? অথবা বিশ্বকূটনীতি কোন ভিত্তির উপরে চলবে? ইত্যাদি কোন প্রশ্নেরই উত্তর তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে এদের তৈরি করা হয়নি; তাই এদের কাছে কোন সমস্যারই সমাধান নেই। এদের তৈরি করা হচ্ছে ধর্মান্ধ হিসেবে; আদর্শিক চিন্তার অনুসারী হিসেবে নয়। ইসলাম যে একটা আদর্শ, সেটাই এদের কাছে কোনদিন পরিষ্কার করা হবে না। কারণ সেটা হলে তো গেম নষ্ট হয়ে যাবে; সেম-সাইড গোল হবে!
আদর্শিক শক্তির কার্যকলাপ বোঝার সময় হয়েছে
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব আদর্শিক দিক থেকে চিন্তা করে। তারা তাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সবকিছু করে এবং করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না পৃথিবীর কোথাও তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হোক। যেখানেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের গন্ধ সে পাবে, সেখানেই সে ঝামেলার সৃষ্টি করবে। ‘জঙ্গী-জঙ্গী’ খেলাটাও এই আদর্শিক যুদ্ধেরই অংশ। এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জার আদর্শকে খারাপভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাই শুধু করা হয়না, একইসাথে সেই আদর্শের রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া নষ্ট করা হয়। একটা ভুল আদর্শকে would-be রিক্রুটদের কাছে তুলে ধরা হয়, যাতে তারা সঠিক রাস্তা থেকে সরে আসে। আর একইসাথে ওই বেঠিক রাস্তায় গমনকারীদের ধ্বংস করার জন্যে ওই দেশের মানুষকেই ট্রেনিং দেয়া হয়, টাকাপয়সা দেয়া হয়, অস্ত্রসস্ত্র দেয়া হয়। আক্রান্ত দেশ এসব কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকবে যে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা হারাবে। আর চাপের মুখে তাদেরকে পশ্চিমাদের হাত ধরে সাহায্য চাইতে বাধ্য করা হবে। এই কাহিনী কোন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। এগুলি মার্কিনীরা ঠান্ডা যুদ্ধের সময় দেশে দেশে করেছে; এদেশেও করেছে। আবারও করতে যাচ্ছে।
১৯৭০-এর দশকে এই দেশে একটা বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা হয়, যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িত হতে যাওয়া (would-be communist) শিক্ষিত এবং মেধাবী তরুণদের দলে ভেড়াতো। এরা নিজেদের বাম বলে দাবি করলেও এরা আসলে কমিউনিজমের আদর্শকে অন্য দিকে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল, যে দিকে গেলে কমিউনিজমের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তারা এক সশস্ত্র সংগ্রামে এই তরুণদের জড়িত করেছিল, যেই সংগ্রামের প্রকৃতপক্ষে কোন উদ্দেশ্য আজ অবধি কেউ বের করতে পারেনি। কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান ছাড়াই এরা বছরের পর বছর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে বিশেষ বাহিনীও তৈরি করা হয়, যেটাতে পশ্চিমাদের ছায়া সমর্থন ছিল। অর্থাৎ সংঘাতের উভয় পক্ষেই পশ্চিমাদের ইন্ধন ছিল। এভাবে দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণদেরকে আলাদা করে ফায়ারিং স্কোয়াডে নেবার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ কমিউনিজমকে ঠেকানো যায়। হাজার হাজার তরুনকে এভাবে বলি দেয়া হয়।
১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পশ্চিমাদের আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী যে ইসলাম তা এখন মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছেন। মুসলিম দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে পশ্চিমা আদর্শের প্রতি হুমকিস্বরূপ, তা এর আগেও লিখেছি। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বাইপ্রোডাক্ট হচ্ছে বিরাট সংখ্যক তরুণ (প্রধানতঃ ১৫ থেকে ২৪ বছর), যারা কিনা যেকোন আন্দোলনে সামনে থাকে, কারণ তাদের রক্ত গরম এবং কর্মশক্তি প্রচুর। যেহেতু জনগণকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা প্রসেসের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তাই এটা তাদের জানা ছিল যে কিছুকাল পরেই মুসলিম সমাজে তরুণদের সংখ্যা কমতে থাকবে। তখন সেই জাতি আস্তে আস্তে পশ্চিমাদের হুমকি হিসেবে থাকবে না। সেই সময়টা পার হওয়ার আগ পর্যন্ত এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রেখে জেনারেশনটা নষ্ট করাই উদ্দেশ্য।
এ এক “আদর্শিক ফোড়া” মাত্র
জঙ্গীবাদ বা এধরনের কার্যকলাপ হলো “আদর্শিক ফোড়া” (Ideological Furuncle)। আইসিস-ও এই একই ফোড়ার অংশ। এক আদর্শিক শক্তি অন্য আদর্শের উত্থান ঠেকাতে এরকম “ফোড়া”র জন্ম দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই ব্রিটিশরা চিন্তা করতে শুরু করে যে মধ্যপ্রাচ্যে একটা ইহুদী রাষ্ট্র তৈরি করে দেয়া যাক, যা কিনা বাকি জীবন মুসলিমদের শরীরে “ফোড়া”র মতো কাজ করবে। সারাজীবন এই “ফোড়া” চুলকাতে তার দুই হাত ব্যস্ত থাকবে। আর পশ্চিমারাও এই “ফোড়া”কে জিইয়ে রাখবে ইন্ধন যুগিয়ে। আর মুসলিমদের আলাদা করে দুর্বল করে রাখা হবে, যাতে তারা এই “ফোড়া”কে কেটে ফেলতে না পারে। আর “ফোড়া” নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিজেদের শক্তিশালী করে একত্রিত করার কোন সুযোগই যেন তারা না পায়। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হেনরি ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান। ইহুদী রাষ্ট্র তৈরি করার আদর্শিক পটভূমি তার ১৯০৭ সালের ‘ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান রিপোর্টে’র কিছু কথার মাঝে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য যে তিনি যেসময় এই কথাগুলি বলেছিলেন, তখন জেরুজালেম মুসলিমদের হাতেই ছিল (১১৮৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একনাগারে ৭৩১ বছর)। ব্রিটিশরা মুসলিমদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করেছিল ১৯১৭ সালের ৯ ডিসেম্বর, অর্থাৎ আরও ১০ বছর পর। এরপর প্রায় তিন দশক ধরে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এখানে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণার (১৯৪৮) ভিত্তি তৈরি করা হয়। যাই হোক, তার কথাগুলি ছিল -
“There are people who control spacious territories teeming with manifest and hidden resources. They dominate the intersections of world routes. Their lands were the cradle of human civilizations and religions.
These people have one faith, one language, one history and the same aspirations.
No natural barriers can isolate these people from one another... if per chance, this nation were to be unified into one state, it would then take the fate of the world into its hands and would separate Europe from the rest of the world.
Taking these considerations seriously, a foreign body should be planted in the heart of this nation to prevent the convergence of its wings in such a way that it could exhaust its powers in never-ending wars. It could also serve as a springboard for the West to gain its coveted objects.”
“আদর্শিক ফোড়া”র সমাধান কোথায়?
যারা পশ্চিমাদের কর্মকান্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন, তাদেরকে ভুল পথে প্রবাহিত করারও পদ্ধতি আছে। একটা কনসেপ্ট রয়েছে, যেটাকে মানুষ conspiracy theory বলে জানে। যখনই কেউ পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, তখনই তাকে এমন একটা থিওরি ধরিয়ে দেয়া, যাতে সে খেই হারিয়ে ফেলে এবং কোন সমাধান খুঁজে না পায়। এভাবে সে সবকিছুকেই conspiracy theory বলা শুরু করবে, এমনকি আসলে ঘটে যাওয়া কোন ব্যাপারকেও সে তা-ই মনে করতে থাকবে। একটা ঘটনার পিছনে ৪/৫টা conspiracy theory বানালে শেষ পর্যন্ত সবাই confused হয়ে পড়বে এবং ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এভাবে চোখের সামনে থাকার পরেও সত্যকে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আদর্শিক শক্তির ক্ষমতা যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে না পারে, সেজন্যে আদর্শিক কার্যকলাপকে conspiracy theory-র মাঝে ফেলে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখাটা নিয়ন্ত্রণের একটা পদ্ধতি।
আদর্শিক চিন্তা কতটা শক্তিশালী, তার কিছু উদাহরণ এর আগের লেখাগুলিতে দিয়েছি। আজ আরেকটি দিচ্ছি। ১৯৬২ সালের ‘কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস’ সম্পর্কে কেউ কেউ জেনে থাকবেন। প্রায় সবাই মনে করেন যে সেটার কারণে দুনিয়া পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছে চলে গিয়েছিল। আসলে এটা ছিল ব্রিটেনকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বের করে দেবার জন্যে মার্কিনীদের সাথে সোভিয়েতদের একটা সমন্বিত চেষ্টা, যা অনেকটাই সফল হয়েছিল। এরপর থেকে ব্রিটেনকে বের করে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির লড়াইয়ে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। থার্ড পার্টকে বের করে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এগুলি আদর্শিক চিন্তার ফলাফল, যা বেশিরভাগ মানুষের কাছে conspiracy theory হিসেবেও পৌঁছবে না, বোঝা তো দূরে থাকুক! আদর্শিক গেম হচ্ছে সবচাইতে বড় গেম; এগুলি জাতীয়তার গেম থেকে অনেক অনেক উপরে। ভূরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আদর্শিক শক্তিরা। তাই ভূরাজনীতি বুঝতে হলে আদর্শিক গেম বুঝতে হবে। একুশ শতকে এসে বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন, সেটা বুঝতেও এই গেম বুঝতে হবে; নাহলে হিসেব মিলবে না কিছুতেই! এখন আর ‘বুঝি না ভাই’ বলে হা করে চেয়ে থাকার সময় নেই। গুলশানের ঘটনা মানুষের ঘোর কাটানো যথেষ্ট হওয়া উচিত।
গুলশান ৭৯ নম্বরের কাহিনী হলো আরেক “আদর্শিক ফোড়া”র কাহিনী। আমাদের আজকে যেটা বুঝতে হবে তা হলো আমরা কিভাবে এই “ফোড়া” নির্মূল করবো তা নয়, বরং কি কারণে জোর করে এই ফোড়া তৈরি করার চেষ্টা চলছে সেটা। সেই কারণখানা বুঝতে পারার মাঝেই আছে ফোড়া নির্মূলের চিকিতসা। কারণখানা না বুঝে ফোড়া নির্মূলের চেষ্টা সফল হবে না কোনদিনই। আদর্শিক আক্রমণকে আদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে, নাহলে ফোড়া চুলকাতে চুলকাতেই সারাজীবন পার করতে হবে।
 |
| "জঙ্গী-জঙ্গী" খেলাটা হচ্ছে একটা আদর্শিক খেলা। এই খেলা না বুঝতে পারলে অন্যের আদর্শিক উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করা হবে। একটা "আদর্শিক ফোড়া" তৈরি করে জাতিকে ব্যস্ত রাখাটাই উদ্দেশ্য। |
গুলশান ৭৯ নম্বর রোডের ক্যাফেতে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। এর আগে যা যা নিয়ে লিখেছি, এই ঘটনা তারই চলমান প্রবাহ মাত্র। কিছুদিন আগেই আদর্শিক যুদ্ধের (Ideological Conflict) পুণরাবির্ভাব নিয়ে লিখেছিলাম, যেখানে বলেছিলাম যে পশ্চিমা আদর্শিক চিন্তাবিদ এবং ভূরাজনীতি বিশারদরা কিভাবে চিন্তা করছেন সামনের দিনগুলি নিয়ে। তারা সামনের দিনগুলিতে বিশ্বের Balance of Power-এ ব্যাপক পরিবর্তনের আশংকা করছেন বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তথা পশ্চিমা বিশ্বকে ‘উদ্ভট’ সব কৌশল অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছেন। ‘উদ্ভট’ বলছি আসলে সেগুলি উদ্ভট বলে নয়, বরং সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি উদ্ভট ঠেকবে সেজন্যে। যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে অন্য কথা বললেও দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু স্থানে সে আসলে স্থিতিশীলতা চায় না। স্থিতিশীলতা হচ্ছে একটা শক্তিশালী জাতি গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত। স্থিতিশীল জাতিই চিন্তা করে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের চিন্তার বিকাশের পথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সেই জাতি যদি অবাঞ্ছিত কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে চিন্তা করার সময়ও পাবে না এবং তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভিত্তিগুলিও হবে দুর্বল। এই প্রেক্ষাপটেই আজকে গুলশান ৭৯ নম্বর রোডের ঘটনার মূল্যায়ন করা চেষ্টা করবো।
গুলশান ৭৯ নম্বর – প্রাসঙ্গিক আলোচনা
গুলশানের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। তবে সবকিছু প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় সবকিছু নিয়ে কথা বলবো না। আর circumstantial evidence নিয়ে এখানে বেশি কথা বলতে চাই না, কারণ এগুলি manipulate করা সম্ভব। যেসব ব্যাপার ভূরাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে, শুধু সেসব ব্যাপার নিয়েই কথা বলবো।
প্রথমতঃ এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে এই অপারেশনে “বিদেশী” হওয়াটাই টার্গেট হবার মূল শর্ত ছিল। বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ হত্যা হওয়াটা সেটাই প্রমাণ করে। এখানে বিশেষ কোন শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা বা বিশ্বের সকল সমস্যার মূল বলে ধমকি দেবার মতো কোন রাজনৈতিক মেসেজ ছিল না। অর্থাৎ আক্রমণটা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে ছিল না।
দ্বিতীয়তঃ এক ঘন্টার মাঝে অপারেশন শেষ করে না ফেলে একটা জিম্মি সিচুয়েশনের অবতারণা করে সেটাকে ১০ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখার কি মানে দাঁড়ায়? কেউ কেউ কথা তুলবেন যে আইন-শৃংখলা বাহিনী ১০ ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু যে প্রশ্ন কেউ করবে না তা হলো, জিম্মিকারীদের কি খেয়ে কাজ ছিল না যে ১০ ঘন্টা বসে থাকবে? তারা যদি জানতোই যে তারা মারা পড়বে, তাহলে ১০ ঘন্টা ওখানে বসে ঘুমিয়ে তাদের লাভ কি ছিল? যদি সবাইকে মেরেই ফেলা হবে, তাহলে এত ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখে কিছু লোকের মুখে কথা তুলে দেয়া কেন? কিছু সমালোচক এখন কি করলে কি হতে পারতো, বা কখন কি করা উচিত ছিল, বা কোনটা করা ঠিক হয়নি, এগুলি নিয়ে কথা বলার সুযোগ তৈরি করা কেন? এক্ষেত্রে কথা বলার সুযোগ নিয়ে কে চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছে? জিম্মিকারীরা সেই চাপ সৃষ্টিকারীদের পক্ষেই কাজ করেছে।
তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ কোন পর্যটন কেন্দ্র নয়। এদেশে যে বিদেশীরা আসে, তার ৯০%-এরও বেশি আসে কাজ করতে। বিদেশীরা এদেশে আসেন বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে। কাজের ফাঁকে এরা দেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে আসে। যদি এদেশে বিদেশীদের উপরে হামলা হয়, তাহলে এদেশের পর্যটন শিল্পের কিছু হবে না, বরং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হত্যাকান্ডের শিকার জাপানিরা মেট্রো-রেল প্রজেক্টে কাজ করছিলেন আর ইটালিয়ানরা গার্মেন্টস ব্যবসায়ে ছিলেন; অর্থাৎ সকলেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এখানে এসেছিলেন। আরও নয়জন তাবেলা আর আরও সাতজন কুনিওকে হত্যা করা কেন? এই দু’টি দেশতো যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’ প্রথম সারির অংশগ্রহণকারী দেশ নয়। তাহলে এই দেশগুলিকে কেন টার্গেট করা? ইটালিয়ান এবং জাপানিরা তো অর্থনৈতিক কাজে এখানে আসে। এদের হত্যার মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য কি? কি হাসিল হবে এতে?
চতুর্থতঃ বাংলাদেশ তথা ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটা প্রয়াস মনে হতে পারে এটা। “আল্লাহু আকবার” কথাটাকে কলুষিত করে বেসামরিক বিদেশী হত্যা করে ইসলামকে বাজে ভাবে বাকি বিশ্বের সন্মুখে তুলে ধরার একটা ব্যর্থ প্রয়াস এটা। পশ্চিমা বিশ্বের মানুষই যেখানে প্রতিদিন ইসলামের মাঝে তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে ইসলামকে আলিঙ্গন করছে, সেখানে এধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো hawk-দের আকৃষ্ট করা ছাড়া আর কি অর্জন করা সম্ভব? ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা নয়, বরং পশ্চিমের hawk-দের মুখে কথা তুলে দেয়াটাই এর মূল উদ্দেশ্য। আর এর সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওইসব hawk-দের এজেন্টরা সক্রিয় হবে।
 |
| গুলশানের অপারেশনের পর এখন বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসতে থাকবে। যতক্ষণ পশ্চিমের আদর্শিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা না হবে, ততক্ষণ এই চাপ অব্যাহত থাকবে। এই আক্রমণ ছিল বাংলাদেশকে পশ্চিমের চাপের মাঝে ফেলার রেসিপি। আদর্শিক শক্তির ইচ্ছার বাস্তবায়ন এভাবেই করা হয়। |
বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টির রেসিপি…
লম্বা সময়ে ওখানে বসে থাকার জন্যে পশ্চিমের এজেন্টরা এখন সুযোগ পাবে এই অপারেশনের সমস্যাগুলির কথা বলে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার। আর একইসাথে এদেশে অর্থনৈতিক কাজে আসা বিদেশীদের টার্গেট করে দেশের অর্থনীতির উপরে চাপ সৃষ্টি করে কিছু শর্ত চাপানোর কাজ চলবে। ঠিক যেমনটি ছয় মাস আগেই হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট এবং ফুটবল দলের ট্যুর নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি করে। এবং বিমানে পণ্য রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিশেষ শর্তগুলি চাপানোর কাজ না হবে, ততক্ষণ চাপ অব্যাহত থাকবে।
এখানে প্রকৃতপক্ষে রেস্টুরেন্টের মানুষগুলিকে জিম্মি করা হয়নি, বরং পশ্চিমের হাতে বাংলাদেশকে জিম্মি করার পথ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমারা বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, নিরাপত্তা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো আদর্শিক, যেটা বাস্তবায়নের জন্যেই বরং এই চাপ সৃষ্টি করা।
যাদের নাম দিয়ে এসব কর্মকান্ড চালানো হচ্ছে তারা যে প্রকৃতপক্ষে অন্য কারো সৃষ্টি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো এদের পক্ষে বর্তমান বিশ্বের কোন সমস্যার সমাধানই দেয়া সম্ভব নয়। ইসলাম কি করে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাখে, তা তাদের জানা নেই। তাদেরকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার কি করে সমাধান করবেন? সবার জন্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন কি করে? অথবা মার্কিন ডলার বা বিশ্ব ব্যাংককে কি করে মোকাবিলা করবেন? আন্তর্জাতিক আইন বা সমুদ্র আইন বা আকাশপথ ব্যবহারের আইনের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেবেন? অথবা বিশ্বকূটনীতি কোন ভিত্তির উপরে চলবে? ইত্যাদি কোন প্রশ্নেরই উত্তর তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে এদের তৈরি করা হয়নি; তাই এদের কাছে কোন সমস্যারই সমাধান নেই। এদের তৈরি করা হচ্ছে ধর্মান্ধ হিসেবে; আদর্শিক চিন্তার অনুসারী হিসেবে নয়। ইসলাম যে একটা আদর্শ, সেটাই এদের কাছে কোনদিন পরিষ্কার করা হবে না। কারণ সেটা হলে তো গেম নষ্ট হয়ে যাবে; সেম-সাইড গোল হবে!
 |
| বাংলাদেশের বিশাল মুসলিম জনসংখ্যা পশ্চিমের জন্যে হমকিস্বরূপ; বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণেরা। তাই এদেরকে ফুসলিয়ে বিপথে নিয়ে আবার বিপথগামীদের মারার জন্যে ফোর্স গঠনের জন্যে সাপোর্ট দেয়া হবে। এটাই আদর্শিক গেম, যা এর আগেও বাংলাদেশে হয়েছে ১৯৭০-এর দশকে। সেবার টার্গেট ছিল কমিউনিজম, এবার টার্গেট ইসলাম। |
আদর্শিক শক্তির কার্যকলাপ বোঝার সময় হয়েছে
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব আদর্শিক দিক থেকে চিন্তা করে। তারা তাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সবকিছু করে এবং করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না পৃথিবীর কোথাও তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হোক। যেখানেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের গন্ধ সে পাবে, সেখানেই সে ঝামেলার সৃষ্টি করবে। ‘জঙ্গী-জঙ্গী’ খেলাটাও এই আদর্শিক যুদ্ধেরই অংশ। এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জার আদর্শকে খারাপভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাই শুধু করা হয়না, একইসাথে সেই আদর্শের রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া নষ্ট করা হয়। একটা ভুল আদর্শকে would-be রিক্রুটদের কাছে তুলে ধরা হয়, যাতে তারা সঠিক রাস্তা থেকে সরে আসে। আর একইসাথে ওই বেঠিক রাস্তায় গমনকারীদের ধ্বংস করার জন্যে ওই দেশের মানুষকেই ট্রেনিং দেয়া হয়, টাকাপয়সা দেয়া হয়, অস্ত্রসস্ত্র দেয়া হয়। আক্রান্ত দেশ এসব কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকবে যে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা হারাবে। আর চাপের মুখে তাদেরকে পশ্চিমাদের হাত ধরে সাহায্য চাইতে বাধ্য করা হবে। এই কাহিনী কোন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। এগুলি মার্কিনীরা ঠান্ডা যুদ্ধের সময় দেশে দেশে করেছে; এদেশেও করেছে। আবারও করতে যাচ্ছে।
১৯৭০-এর দশকে এই দেশে একটা বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা হয়, যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িত হতে যাওয়া (would-be communist) শিক্ষিত এবং মেধাবী তরুণদের দলে ভেড়াতো। এরা নিজেদের বাম বলে দাবি করলেও এরা আসলে কমিউনিজমের আদর্শকে অন্য দিকে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল, যে দিকে গেলে কমিউনিজমের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তারা এক সশস্ত্র সংগ্রামে এই তরুণদের জড়িত করেছিল, যেই সংগ্রামের প্রকৃতপক্ষে কোন উদ্দেশ্য আজ অবধি কেউ বের করতে পারেনি। কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান ছাড়াই এরা বছরের পর বছর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে বিশেষ বাহিনীও তৈরি করা হয়, যেটাতে পশ্চিমাদের ছায়া সমর্থন ছিল। অর্থাৎ সংঘাতের উভয় পক্ষেই পশ্চিমাদের ইন্ধন ছিল। এভাবে দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণদেরকে আলাদা করে ফায়ারিং স্কোয়াডে নেবার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ কমিউনিজমকে ঠেকানো যায়। হাজার হাজার তরুনকে এভাবে বলি দেয়া হয়।
১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পশ্চিমাদের আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী যে ইসলাম তা এখন মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছেন। মুসলিম দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে পশ্চিমা আদর্শের প্রতি হুমকিস্বরূপ, তা এর আগেও লিখেছি। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বাইপ্রোডাক্ট হচ্ছে বিরাট সংখ্যক তরুণ (প্রধানতঃ ১৫ থেকে ২৪ বছর), যারা কিনা যেকোন আন্দোলনে সামনে থাকে, কারণ তাদের রক্ত গরম এবং কর্মশক্তি প্রচুর। যেহেতু জনগণকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটা প্রসেসের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তাই এটা তাদের জানা ছিল যে কিছুকাল পরেই মুসলিম সমাজে তরুণদের সংখ্যা কমতে থাকবে। তখন সেই জাতি আস্তে আস্তে পশ্চিমাদের হুমকি হিসেবে থাকবে না। সেই সময়টা পার হওয়ার আগ পর্যন্ত এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রেখে জেনারেশনটা নষ্ট করাই উদ্দেশ্য।
এ এক “আদর্শিক ফোড়া” মাত্র
জঙ্গীবাদ বা এধরনের কার্যকলাপ হলো “আদর্শিক ফোড়া” (Ideological Furuncle)। আইসিস-ও এই একই ফোড়ার অংশ। এক আদর্শিক শক্তি অন্য আদর্শের উত্থান ঠেকাতে এরকম “ফোড়া”র জন্ম দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই ব্রিটিশরা চিন্তা করতে শুরু করে যে মধ্যপ্রাচ্যে একটা ইহুদী রাষ্ট্র তৈরি করে দেয়া যাক, যা কিনা বাকি জীবন মুসলিমদের শরীরে “ফোড়া”র মতো কাজ করবে। সারাজীবন এই “ফোড়া” চুলকাতে তার দুই হাত ব্যস্ত থাকবে। আর পশ্চিমারাও এই “ফোড়া”কে জিইয়ে রাখবে ইন্ধন যুগিয়ে। আর মুসলিমদের আলাদা করে দুর্বল করে রাখা হবে, যাতে তারা এই “ফোড়া”কে কেটে ফেলতে না পারে। আর “ফোড়া” নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিজেদের শক্তিশালী করে একত্রিত করার কোন সুযোগই যেন তারা না পায়। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হেনরি ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান। ইহুদী রাষ্ট্র তৈরি করার আদর্শিক পটভূমি তার ১৯০৭ সালের ‘ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান রিপোর্টে’র কিছু কথার মাঝে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য যে তিনি যেসময় এই কথাগুলি বলেছিলেন, তখন জেরুজালেম মুসলিমদের হাতেই ছিল (১১৮৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একনাগারে ৭৩১ বছর)। ব্রিটিশরা মুসলিমদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করেছিল ১৯১৭ সালের ৯ ডিসেম্বর, অর্থাৎ আরও ১০ বছর পর। এরপর প্রায় তিন দশক ধরে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এখানে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণার (১৯৪৮) ভিত্তি তৈরি করা হয়। যাই হোক, তার কথাগুলি ছিল -
“There are people who control spacious territories teeming with manifest and hidden resources. They dominate the intersections of world routes. Their lands were the cradle of human civilizations and religions.
These people have one faith, one language, one history and the same aspirations.
No natural barriers can isolate these people from one another... if per chance, this nation were to be unified into one state, it would then take the fate of the world into its hands and would separate Europe from the rest of the world.
Taking these considerations seriously, a foreign body should be planted in the heart of this nation to prevent the convergence of its wings in such a way that it could exhaust its powers in never-ending wars. It could also serve as a springboard for the West to gain its coveted objects.”
“আদর্শিক ফোড়া”র সমাধান কোথায়?
যারা পশ্চিমাদের কর্মকান্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন, তাদেরকে ভুল পথে প্রবাহিত করারও পদ্ধতি আছে। একটা কনসেপ্ট রয়েছে, যেটাকে মানুষ conspiracy theory বলে জানে। যখনই কেউ পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, তখনই তাকে এমন একটা থিওরি ধরিয়ে দেয়া, যাতে সে খেই হারিয়ে ফেলে এবং কোন সমাধান খুঁজে না পায়। এভাবে সে সবকিছুকেই conspiracy theory বলা শুরু করবে, এমনকি আসলে ঘটে যাওয়া কোন ব্যাপারকেও সে তা-ই মনে করতে থাকবে। একটা ঘটনার পিছনে ৪/৫টা conspiracy theory বানালে শেষ পর্যন্ত সবাই confused হয়ে পড়বে এবং ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এভাবে চোখের সামনে থাকার পরেও সত্যকে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আদর্শিক শক্তির ক্ষমতা যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে না পারে, সেজন্যে আদর্শিক কার্যকলাপকে conspiracy theory-র মাঝে ফেলে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখাটা নিয়ন্ত্রণের একটা পদ্ধতি।
আদর্শিক চিন্তা কতটা শক্তিশালী, তার কিছু উদাহরণ এর আগের লেখাগুলিতে দিয়েছি। আজ আরেকটি দিচ্ছি। ১৯৬২ সালের ‘কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস’ সম্পর্কে কেউ কেউ জেনে থাকবেন। প্রায় সবাই মনে করেন যে সেটার কারণে দুনিয়া পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছে চলে গিয়েছিল। আসলে এটা ছিল ব্রিটেনকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বের করে দেবার জন্যে মার্কিনীদের সাথে সোভিয়েতদের একটা সমন্বিত চেষ্টা, যা অনেকটাই সফল হয়েছিল। এরপর থেকে ব্রিটেনকে বের করে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির লড়াইয়ে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। থার্ড পার্টকে বের করে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এগুলি আদর্শিক চিন্তার ফলাফল, যা বেশিরভাগ মানুষের কাছে conspiracy theory হিসেবেও পৌঁছবে না, বোঝা তো দূরে থাকুক! আদর্শিক গেম হচ্ছে সবচাইতে বড় গেম; এগুলি জাতীয়তার গেম থেকে অনেক অনেক উপরে। ভূরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আদর্শিক শক্তিরা। তাই ভূরাজনীতি বুঝতে হলে আদর্শিক গেম বুঝতে হবে। একুশ শতকে এসে বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন, সেটা বুঝতেও এই গেম বুঝতে হবে; নাহলে হিসেব মিলবে না কিছুতেই! এখন আর ‘বুঝি না ভাই’ বলে হা করে চেয়ে থাকার সময় নেই। গুলশানের ঘটনা মানুষের ঘোর কাটানো যথেষ্ট হওয়া উচিত।
গুলশান ৭৯ নম্বরের কাহিনী হলো আরেক “আদর্শিক ফোড়া”র কাহিনী। আমাদের আজকে যেটা বুঝতে হবে তা হলো আমরা কিভাবে এই “ফোড়া” নির্মূল করবো তা নয়, বরং কি কারণে জোর করে এই ফোড়া তৈরি করার চেষ্টা চলছে সেটা। সেই কারণখানা বুঝতে পারার মাঝেই আছে ফোড়া নির্মূলের চিকিতসা। কারণখানা না বুঝে ফোড়া নির্মূলের চেষ্টা সফল হবে না কোনদিনই। আদর্শিক আক্রমণকে আদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে, নাহলে ফোড়া চুলকাতে চুলকাতেই সারাজীবন পার করতে হবে।