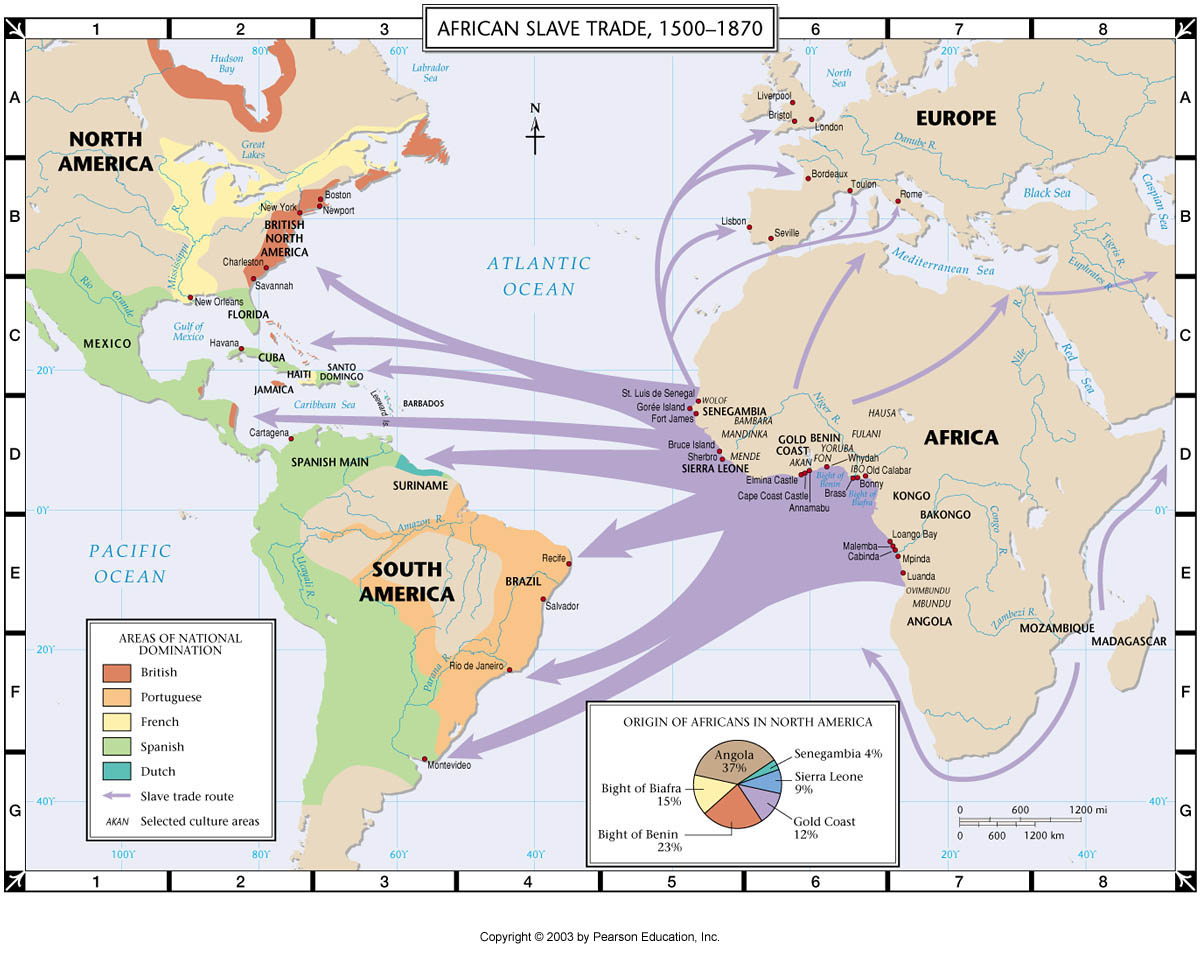২৮ আগস্ট ২০১৫
কিছুদিন আগে মার্কিন জিওস্ট্র্যাটেজিস্ট আলফ্রেড
মাহানের থিওরির উপরে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে বঙ্গোপসাগরে একটি ম্যারিটাইম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব হতে চলেছে। এখন প্রশ্ন এসে পড়ে যে সেটা কিভাবে হবে? কিভাবে হবে, সেটা নিয়ে কথা বলার আগে কিছু কথা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা রাখা জরুরি। মাহান তার চিন্তাতে এনেছিলেন যে, মানুষের চিরাচরিত চিন্তার ফসল আন্তর্জাতিক পরিসরে কিভাবে প্রয়োগ হতে পারে। এক্ষেত্রে যেহেতু ঐতিহাসিক কারণে তিনি পুঁজিবাদী বিশ্বের বাইরে চিন্তা করতে পারেননি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে বিশ্বে এখন শুধু পুঁজিবাদই বিরাজ করছে, তাই মাহানের থিওরি এসময়ে অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারছে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে কারো পক্ষেই হলফ করে বলা যায় না যে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যাবস্থা চিরস্থায়ী হবে। বিশেষ করে পুঁজিবাদের স্পন্সর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি এখন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সামরিক দিক থেকে বিশ্বের উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছে। এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি বেশ দ্রুতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, যা কিনা ভবিষ্যতে বিশ্ব নেতৃত্বতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। তখন পুঁজিবাদ সহ বা পুঁজিবাদ ছাড়া বিশ্বের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, সেটা এখন বলা দুষ্কর। চীন এখন তার সমাজতন্ত্রকে ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদ থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু সুবিধা নিয়ে দেশকে গড়ার চেষ্টায় রয়েছে। চীন, জাপান এবং জার্মানি-সহ অনেক দেশ এখন মার্কেন্টিলিস্ট ইকনমি অনুসরণ করছে, যার অর্থ হচ্ছে, রপ্তানির পিছনে সর্বশক্তি নিয়োগ, অথচ আমদানি নিরুতসাহিত করা। এই নীতি ইউরোপিয়রা অনুসরণ করেছিল কয়েকশ’ বছর, যখন তারা উপনিবেশগুলিকে নিজেদের তৈরি পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিল এবং একেবারে বেসিক কাঁচামাল ছাড়া উপনিবেশের তৈরি যেকোন জিনিসের উপরে উচ্চ কর আরোপ করেছিল। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অগ্রপথিক ব্রিটেন এবং আমেরিকা নিজেরাও নিজেদের কৃষকদের ভর্তুকি দেয়, যা কিনা মুক্ত বাজারের নীতি-বিরূদ্ধ। যাইহোক, সামনের দিনগুলিতে মাহানের থিওরি পুরোপুরি কাজ করবে, সেটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। তবে এটাও ঠিক মাহানের থিওরির কিছু ব্যাপার মানুষের জন্মগত কিছু চাহিদাকে ঘিরে, যেকারণে সমাজব্যাবস্থা এবং সরকার নির্বিশেষে সেগুলি বাস্তবে রূপ নেবার সম্ভাবনা প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ, যেকোন মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে সে কিন্তু শক্তভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করে – ঠিক যেমনটি হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। এমন অবস্থায় এদেশের মানুষ সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট কাজে লাগিয়ে বঙ্গোপসাগরে (এবং বঙ্গোপসাগর পার হয়ে) পাড়ি জমাবে।
 |
| বহিঃবাণিজ্য-নির্ভরতা বাংলাদেশকে ঠেলে দিচ্ছে এমন একদিকে যেখানে অনেকেরই পা
মাড়াতে বাধ্য হবে দেশ। এমতাবস্থায় শক্ত নেতৃত্ব না দিতে পারলে দেশ মহা
বিপদে পড়বে |
পুঁজিবাদ এবং পরিবর্তিত বাংলাদেশ
ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া বহিঃবাণিজ্য-নির্ভর বাংলাদেশ তার বিশাল জনসংখ্যার চাপেই বঙ্গোপসাগরকে নিজেদের সাগর হিসেবে দেখতে শুরু করবে। বহিঃবাণিজ্যের উপরে ব্যাপক নির্ভরশীলতার কারণে বাণিজ্য রক্ষা করাকে সে তার বেঁচে থাকার প্রধান কর্মকান্ডের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। বিশ্বে পুঁজিবাদ না থাকলেও বাংলাদেশের মানুষ এদিকেই এগুবে, কারণ ব্রিটিশদের চিন্তা এবং কর্মকান্ডের (প্রধাণত ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ সংক্রান্ত কর্মকান্ড) কারণে ভবিষ্যতে কখনো এদেশের মানুষের পুরোপুরি স্বনির্ভর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বেঁচে থাকার জন্যে জরুরি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বেসিক কাঁচামালের উতস এখন বাংলাদেশে নেই এবং ভবিষ্যতেও সেটার তৈরি হবার সম্ভাবনা কম। এখন এটা বলাই বাহুল্য যে সরকারের নীতি এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখবে; কিন্তু কিছু ব্যাপার সংঘটিত হবে মানুষের প্রকৃতিগত চাপে, যা কিনা সরকারের পক্ষে আটকানো কঠিন, অথবা সরকারই বাধ্য হবে মানুষের দেখভালের অংশ হিসেবে কিছু পদক্ষেপ নিতে, যা কিনা সে আগে কখনো নেয়নি। এসব পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করবে সরকারের আন্তরিকতার উপরে এবং বহিঃশক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উপরে। প্রথম কারণটি অবশ্য অনেকাংশেই দ্বিতীয়টির উপরে নির্ভরশীল থাকবে জিওপলিটিক্সের কারণে। এদেশের মানুষ সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট কাজে লাগিয়ে যেসব কাজ করবে, তা বঙ্গোপসাগর, তথা ভারত মহাসাগর, তথা এশিয়া, তথা পুরো বিশ্বের স্ট্র্যাটেজিক ব্যালান্সে প্রভাব ফেলবে। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বশক্তিদের ব্যাপক আগ্রহের কারণ হবে। এরকম বাস্তবতায় শক্তিশালী এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাব ঘটলে দেশ মহাবিপদে পতিত হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর যাই হোক, মানুষকে নিজের স্বার্থ জ্বলাঞ্জলি দিতে শেখায় না। নেতৃত্বের দৃঢ়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। নির্ভরশীলতার উপরে স্বাধীনতা দাঁড়িয়ে থাকে না।
নেতৃত্ব ও নীতি
উপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলি বুঝেই বাংলাদেশকে এগুতে হবে। বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারা থেকে শুরু করে সামনের দিনগুলিকে কি কি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি চিন্তা করেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশ্বরাজনীতি এবং বিশ্বঅর্থনীতিতে সম্ভাব্য পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো মানসিকতা তৈরি এবং প্রস্তুতি নেবার দায়িত্বও নেতৃত্বের। এক্ষেত্রে মানুষের বৃহত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাক্তি এবং বহিঃস্বার্থকে পিছনে ফেলে নীতি নির্ধারণের মাঝেই আসল সাফল্য নিহিত থাকবে। ম্যারিটাইম দেশ গঠনে কেন, দেশের যেকোন নীতি নির্ধারণেই এই বিষয়গুলি প্রাধাণ্য পাওয়া উচিত। আর দেশের ভেতরে যা কিছু ঘটবে, তার সবকিছুই ম্যারিটাইম ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের নদনদী সঠিকভাবে ড্রেজিং-এর পরে এর প্রভাব পড়বে পুরো অর্থনীতিতে, এবং সেটার কারণে বহিঃবাণিজ্য থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণ, কূটনীতি, এমনকি সামরিক প্রস্তুতিতেও আসবে পরিবর্তন। এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি নিতে পারার ক্ষমতা শুধু সেধরণের নেতৃত্বেরই থাকবে, যারা কিনা আলফ্রেড মাহান এবং অন্যান্য বিখ্যাত থিওরিস্টরা যেসব বেসিক প্রশ্নের উপরে নির্ভর করে তাদের চিন্তাভাবনাকে এগিয়েছিলেন, সেসব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজে পাবেন, এমনকি দরকার বিশেষে ব্যাকরণ পরিবর্তন করার সক্ষমতা এবং সাহস রাখবেন।
যারা
এর আগের লেখাটি পড়ে মনে করছেন যে বাংলাদেশ নিয়ে এরকম চিন্তা করাটা অবান্তর, তাদের জন্যে শুধু এটাই বলতে চাই যে তারা খুব সম্ভবত ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং আরও কিছু জিনিসের সমন্বয়ে তৈরি খিচুরির স্বাদ নেননি; এই খিচুরির নামই হচ্ছে জিওপলিটিক্স। হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং পর্তুগালের মতো ছোট্ট দেশগুলিও একসময় ঔপনিবেশিক শক্তি ছিলো। ব্রিটিশ ভারতে মাত্র কয়েক হাজার ব্রিটিশ শাসন করতো কোটি কোটি ভারতীয়কে। আসলে যারা এগুলির গভীরতা বুঝতে অক্ষম, তারা সামনের দিনগুলিতে এদেশের নীতি তৈরিতেও অক্ষমতার পরিচয় দেবেন। সঠিক দূরদর্শী নীতিতে অনেক কিছুই থাকতে পারে, যার সবকিছু একবারে লিখে শেষ করা কঠিন। এই লেখার মাধ্যমে এ ধরণের পদক্ষেপগুলির উপরে আলোচনা শুরু করতে পারি কেবল। আজ শুরু করে সামনের দিনগুলিতে আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলার প্রয়াস রাখছি।
 |
| ম্যারিটাইম দেশ হবার জন্যে বাংলাদেশের কাছে তার সবচাইতে বড় সম্পদ হলো বিরাট
জনসংখ্যা। সামনের দিনগুলিতে এই জনসম্পদকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়াটা জরুরি |
জনসংখ্যা সমস্যা, নাকি জনসম্পদ?
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ভেতরে সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে এর জনসংখ্যা। একসময় বাইরে থেকে প্রচুর ডলার এসেছে এদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে। অথচ এখন জনসংখ্যার কারণেই বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের অনেকগুলি দেশ এখন সামনের দিনগুলিতে শক্তিশালী দেশরূপে আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফল হিসেবে পশ্চিমা দেশগুলি এখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রন হারাতে বসেছে এবং নিজেদের সম্ভুক গতির অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সারা বিশ্ব থেকে জনশক্তি আমদানি করে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাংলাদেশকে ম্যারিটাইম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনশক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করাটা জরুরি। মাহান ডাচদের উদাহরণ দিয়েছিলেন - কিভাবে তারা একটা ম্যারিটাইম দেশে পরিণত হয়। ডাচদের চিন্তাশীল লোকেরা হিসেব করে বের করেছিলেন যে হল্যান্ডের ভূখন্ডের পক্ষে তাদের জনসংখ্যার মাত্র আট ভাগের এক ভাগের ভরণপোষণ যোগান দেওয়া সম্ভব। ডাচরা প্রথমে সাগরে মাছ ধরতে বের হলো। এরপরে তার মাছ প্রসেসিং করতে শিখলো এবং সেই প্রসেস করা মাছ ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতে শুরু করলো। এক্ষেত্রে ইউরোপের উপকূলের ঠিক মাঝামাঝি হওয়ায় এবং রাইন নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় গোটা ইউরোপের সাথে চমতকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের সাহায্য করেছিল। খুব শিগগিরই ডাচরা নাবিকের জাতি হয়ে উঠলো। একসময় স্প্যানিশ রাজের বেশিরভাগ জাহাজই ডাচরা চালাতো। নিজেদের দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পও গড়ে উঠতে থাকলো বাণিজ্যের সাফল্যের সাথে সাথে। এভাবে ডাচদের বিরাট এক বাণিজ্য নৌবহর গড়ে উঠলো, যা কিনা ইউরোপে বাণিজ্য করতে গিয়ে অন্যান্য শক্তিশালী দেশের স্বার্থের রোষানলে পড়লো এবং জলদস্যুদের কবলেও পড়তে থাকলো। এভাবেই ডাচরা তৈরি করলো তাদের নৌবাহিনী এবং নৌ-নিরাপত্তা, যা কিনা পরবর্তীতে তাদেরকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বিশ্ব আবিষ্কারের স্পৃহা যোগায় এবং এক ঐপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত করে। এখানে ডাচদের দ্রুত বর্ধনশীল জনস্ংখ্যা এবং দেশে অভাবের কারণে জাহাজের নাবিক হবার জন্যে অনেক মানুষ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় বেশি জনসংখ্যার চাপেই তারা বাণিজ্য জাহাজ তৈরিতে মনোনিবেশ করে। জনসংখ্যা একেবারে কম থাকলে কিন্তু ডাচরা সমুদ্রে আধিপত্য লাভের চেষ্টাই করতে পারতো না। সমুদ্র তাদেরকে কর্মসংস্থান এবং নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সমুদ্র দেখে তারা ভয় পায়নি; বরং এই নতুন এডভেঞ্চারকে তারা তাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছে।
 |
| ডাচদের উত্থানের পিছনে তাদের ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি একটা বিরাট ভূমিকা রাখে।
সমুদ্রের দিকে ডাচদের আগ্রহী করে তোলার জন্যে মাছ আহরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ
কারণ ছিল |
মাছ থেকে উপনিবেশ – ডাচদের উত্থান
ডাচদের জনশক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে মূলত জাহাজ, জাহাজ-নির্মাণ, মাছ আহরণ, সমুদ্র-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারখানা, নৌবাহিনী, ইত্যাদিতে সেক্টরে। অনেকেই আবার বিশ্বব্যাপী ডাচদের স্থাপিত ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে জীবিকা খুঁজে নিয়েছে। এই প্রতিটা সেক্টরেই বিপুল জনসম্পদের দরকার ছিল তাদের। ডাচদের কাছ থেকে শেখার রয়েছে বাংলাদেশেরও। রাইনের সবগুলি শাখানদী হল্যান্ডের মাঝ দিয়ে সমুদ্রে পড়ায় ডাচরা এমনিতেই পানির দেশের মানুষ ছিল। নদীপথে ডাচরা জার্মানিসহ এবং ইউরোপের অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য করতো; এখনও ডাচরা নদী এবং খাল ব্যবহার করে নিজেদের বেশিরভাগ পণ্য পরিবহণ করে এবং জার্মানিতে রপ্তানি করে। বাংলাদেশের দু’টি বিশাল নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র ব্রিটিশরা মানচিত্রে কেটে দিয়ে গেছে, যাতে এখানে রাইনের মতো কোন শক্তিশালী নদীপথের উত্থান না হয়। ব্রিটিশরা চলে যাবার পরে তাদের মিত্র ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে, যা নিয়ে এর আগের লেখায় বিস্তারিত লিখেছি। নদীপথে ডাচদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরাট লাভবান হলেও আমরা এই উদাহরণটুকু কাজে লাগাতে পারছি না। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথকে কাজে লাগাতে মনোনিবেশ করতে পারি।
ক্যাপিটাল ড্রেজিং করার মাধ্যমে পুরাতন নদীপথগুলিকে জীবন দিতে পারি আমরা। ড্রেজার এবং এর আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং বালুবাহী জাহাজ তৈরি করতে গিয়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্প চাঙ্গা হবে। রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, চাপাই নবাবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, সিলেট, ইত্যাদি শহরকে নদীপথে পুণরায় যুক্ত করতে পারলে দেশের ভেতরে শিল্প এবং বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ হবে এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প আরও একটা অণুপ্রেরণা পাবে। ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনাল সরকারীভাবে একটা তৈরি করা হলেও আরও দরকার নদনদীর পাশে। এখন পর্যন্ত এসব টার্মিনালে ব্যবহৃত হবে বলে অনেক কনটেইনাল জাহাজ দেশীয় শিপইয়ার্ডগুলিতে তৈরি হচ্ছে। এই জাহাজগুলি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার ঢাকার আশেপাশের জায়গায় পরিবহণ করবে এবং ব্যয়বহুল ও যনজটপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েকে বাইপাস করবে। নদীপথগুলি উন্মুক্ত করা গেলে দেশের অনেকস্থানে নদীর তীরে খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল এবং রাসায়নিক সারের গুদাম তৈরি করা যাবে; এতে দেশীয় জাহাজ আরও দেখা যাবে। যাত্রীবাহী জাহাজের সংখ্যাও বাড়বে একইসাথে; মানুষ ব্যয়বহুল সড়কপথের উপরে নির্ভর না করে সাশ্রয়ী নৌপথের দিকেই যাবে। একই সাথে ছোট-বড় সকল ধরনের পণ্যবাহী জাহাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণের জন্যে ফিশিং ট্রলার তৈরি করা শুরু হয়েছে কেবল; এর সংখ্যা সামনের দিনগুলিতে আরও বাড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাহাজ শিল্পের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে রয়েছে লাইটার জাহাজ; এরকম হাজার খানেক জাহাজ চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর থেকে তেল এবং অন্যান্য পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এই নৌ-পরিবহণ শিল্প যেন অটুট থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখাটা জরুরি। কোন ধরনের সরকারী বা বেসরকারী প্রজেক্ট যদি এই নৌপরিবহণের বিকল্প তৈরি করতে চায়, সেটা প্রতিরোধ করাটা দেশের ম্যারিটাইম ভবিষ্যতকে চিন্তা করে জরুরী কর্তব্য।
 |
| বাংলাদেশের বাণিজ্য জাহাজের ক্ষুদ্র বহর যেভাবে কমছে, তাতে জাতীয়
নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। দেশের নেতৃত্ব ম্যারিটাইম দেশের স্বপ্ন
দেখতে চাইলে মার্চেন্ট নেভি নিয়ে ভাবতে হবে এখনই। |
বাংলাদেশের মার্চেন্ট নেভির গুরুত্ব
তবে এইসকল জাহাজই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌপথের জন্যে জাহাজ (ফিশিং ট্রলার বাদে)। এগুলি জাহাজে কর্মসংস্থান হতে কাউকে সমুদ্রের সাথে অভ্যস্ত হতে হয় না। ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা ছিল ২৪টি। ওই বছর দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধন সহজ করা হয় এবং শুল্ক কমানো হয়।এর ফলশ্রুতিতে চার বছরে নতুন যুক্ত হয় ৪৭টি জাহাজ। কিন্তু বিশ্বমন্দায় পড়ে জাহাজ মালিকেরা তাদের জাহাজগুলি স্ক্র্যাপ করে ফেলতে থাকেন। যেখানে ২০১৩ সালে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮-এ, সেটা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৩৮-এ; এবং সামনের দিনগুলিতে সেটা আরও কমতে যাচ্ছে। সরকারী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ এখন মাত্র ৫টি, যা ’৯০-এর আগে ছিল ৩৮টি! ২০১২ সালে যেখানে দেশী জাহাজে নাবিক এবং অফিসার ছিল ১,৬০০, সেটা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি মাত্র ৮০০-তে এসে ঠেকেছে।২০১৪ সালের এক হিসাব অনুযায়ী দেশে ৮৫০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাবিক ও অফিসার বেকার রয়েছে। নৌ একাডেমিগুলা প্রতিবছরই আরও নাবিক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। সরকারী এবং বেসরকারী প্রায় সব জাহাজই অনেক পুরোনো। পুরোনো জাহাজ পশ্চিমা দেশগুলির বন্দরগুলিতে ভিড়তে পারেনা; তাই এই জাহাজগুলি শুধু এশিয়া এবং আফ্রিকার কিছু দেশগুলিতেই যেতে পারে। আর পুরোনো বিধায় জাহাজগুলির মেইনটেন্যান্স খরচ বেশি, যা কিনা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে কঠিন। এরই মধ্যে বিশ্বমন্দার কারণে শিপিং কোম্পানিগুলির লোকসান আরও বেড়ে যায়। এসব জাহাজের প্রায় সবই বাল্ক কার্গো ক্যারিয়ার; কনটেইনার জাহাজ একটাও নেই। অর্থাৎ প্রতিবছর চট্টগ্রাম বন্দর যে ১৬ লক্ষ টিইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে, তার পুরোটাই বিদেশী জাহাজে পরিবহণ করা হয়। বিদেশী জাহাজের শিপিং চার্জ ব্যয়বাবদ বাংলদেশ প্রতিবছর ৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে, যা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারের সামনে সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশ কি সব সামুদ্রিক বাণিজ্য জাহাজ হারাবে, নাকি এই নৌবহরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে? সরকার সবকিছুতে টাকা-পয়সার লাভ-লোকসানের হিসাব করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সরকার লাভ-লোকসান চিন্তা করলে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য চিন্তা থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেবার কথা; কৃষিতে ভর্তুকি দেবার চিন্তাও সরকার করতো না কখনো। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার শুধু টাকার চিন্তা করবে কেন? ম্যারিটাইম দেশ গড়াটা বাংলাদেশের মানুষের জন্যে সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট। এখানে সরকার যদি মানুষিকে ঠিকমতো পথপ্রদর্শন না করে, তাহলে দেশের বিপদ আসন্ন। আর ম্যারিটাইম দেশ গড়ার পেছনে একটা বিশাল অবদান থাকবে এই বাণিজ্যিক নৌবহর বা মার্চেন্ট নেভির। বঙ্গোপসাগরে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ জিওপলিটিক্যাল ঘটনা বাংলাদেশের বিরূদ্ধে যায়, তাহলে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়ানো মার্চেন্ট জাহাজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ সরকার বিপদের সময়ে অন্য কোন দেশ, সংস্থা বা মানুষের উপরে নির্ভর করতে পারে না, যেখানে এই বাণিজ্যপথের সাথে দেশের মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। এধরনের একটা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় সরকার উপেক্ষা করতে পারে না কোনভাবেই।
 |
| ফকল্যান্ড যুদ্ধ। সিভিলিয়ান লাইনার 'ক্যানবেরা'-কে এসকর্ট করছে রয়্যাল নেভির ফ্রিগেট 'এন্ড্রোমিডা'। ক্যানবেরা ৩,০০০ সৈন্য পরিবহণ করে ফকল্যান্ডে নিয়ে যায়। একটা দেশের জাতীয় নিরাপত্তায় বেসামরিক জাহাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এটি। |
বেসামরিক জাহাজ এবং জাতীয় নিরাপত্তা
১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের নৌবাহিনীর কাছে সৈন্য পরিবহণের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক জাহাজ ছিল না। তখন তারা ‘কুইন এলিজাবেথ-২’ নামের একটা যাত্রীবাহী ক্রুজ লাইনার ব্যবহার করে ৫ম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ৩,০০০ সৈন্যকে পরিবহণ করতে। এই উদাহরণ যদি একমাত্র উদাহরণ হতো তাহলেও হতো। আসলে বেসামরিক জাহাজ ব্যবহার করে সামরিক সরঞ্জাম এমনকি সৈন্য পরিবহণের ঘটনা বহু রয়েছে। আর শুধু সামরিকই বা কেন? একটা দেশকে সমুদ্র অবরোধের মধ্যে ফেললে সেই জনগোষ্ঠী যদি না খেয়ে মারা যেতে থাকে, সেটা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় বৈকি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশরা আশংকাজনকভাবে জার্মান সাবমেরিনের কাছে তাদের বাণিজ্য জাহাজগুলি হারাতে থাকে। যে হারে জাহাজ বানানো যাচ্ছিল, তার চাইতে আরও বেশি গতিতে জাহাজ চলে যাচ্ছিল আটলান্টিকের নিচে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভর্তি হয়ে আসা এই জাহাজগুলি কোন রকমে ব্রিটেনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জার্মান সাবমেরিনগুলি ব্রিটেনকে না খাইয়ে মারার চেষ্টায় ছিল; সামরিক-বেসামরিকের কোন বাছ-বিচার ছিল না সেখানে। যুদ্ধের সময়ে এই বাছ বিচার নিয়ে সর্বদাই সমস্যা হয়। বাণিজ্যিক অবরোধের কথা বললে কোন পণ্য বেসামরিক আর কোনটা সামরিক সেটাও তো আলাদা করা সম্ভব হয় না। একই পণ্যের সামরিক এবং বেসামরিক ব্যবহার থাকতে পারে। আবার বেসামরিক পণ্যের মাঝে সামরিক পণ্যও থাকতে পারে। এসব বিষয় চিন্তাতে আনার অর্থই হচ্ছে - বাণিজ্যিক অবরোধে আসলে কেউই পার পায় না। নিজেদের দেশের উপরে অন্য কোন বহিঃশক্তি বাণিজ্যিক অবরোধ দিয়ে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাবে – এটা চিন্তা করাটা যতটা অবান্তর, ঠিক তেমনিভাবে বাণিজ্যিক অবরোধে পরার ভয়ে দেশের জাতীয় সত্তা বিকিয়ে দিয়ে বহিঃশক্তিকে তোয়াক করাটাও দেশদ্রোহিতার শামিল। পশ্চিমা দেশগুলি আর যাই হোক এসব বাস্তবতা পার হয়ে এসেছে। তাদের তাত্ত্বিক চিন্তা তাদেরকে অনেক গভীরে নিয়েছে। গভীর থেকে চিন্তা করার ফলেই তাদের জাতীয় নীতি সকল ক্ষেত্রে একই পথ অনুসরণ করেছে। অপরদিকে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলি পশ্চিমাদের অধীনে থাকার ফলে চিন্তাগত দিক থেকে কোন গভীরতাতেই পৌঁছাতে পারেনি। আন্তর্জাতিক রীতি, পার্শ্ববর্তী দেশের চোখ-রাঙ্গানি, পরাশক্তির-সমর্থিত সাহায্য সংস্থার বৈরি আচরণ ইত্যাদি কথা চিন্তা করে এই দেশগুলি জাতীয় স্বার্থকে জ্বলাঞ্জলি দিয়েছে সময়ে সময়ে।
 |
| সান ফ্রান্সিস্কো-এর কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ডিফেন্স
রিজার্ভ ফ্লীট'এর একাংশ। পুরোনো এই জাহাজগুলি রেখে দেওয়া হয় বছরের পর বছর -
যদি কখনো কাজে লেগে যায়। |
ওল্ড ইজ গোল্ড
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশরা চিন্তা করে শুধুমাত্র একটা ডিজাইনের জাহাজ বানানোর, কিন্তু তাদের শিপইয়ার্ডগুলি তখন প্রচন্ড চাপের মুখে। তাই মার্কিনীরা এই জাহাজগুলি বানাবার দায়িত্ব নিল। ১৮টা আমেরিকান শিপইয়ার্ড ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোট ২,৭১০টা জাহাজ তৈরি করে, যেগুলি ‘লিবার্টি শিপ’ নামে পরিচিত ছিল। ১০,০০০ টন ক্যাপাসিটির এই জাহাজগুলি ১৩৪ মিটার লম্বা ছিল। এসময় বিশাল জাহাজ তৈরি করাটা তেমন সমীচিন ছিল না; কারণ যুদ্ধের মাঝে ডুবে গেলে বড় জাহাজের ক্ষতি পুষানো বেশি কঠিন ছিল। এই জাহাজগুলি তৈরিতে ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভেঙ্গেছে মার্কিনীরা। প্রথম জাহাজটা তৈরি করতে ২৩০ দিন লাগলেও পরবর্তীতে গড় সময় নেমে এসেছিল মাত্র ৪২ দিনে! অর্থাৎ প্রতি ৪২ দিনে একটি করে নতুন জাহাজ তারা ডেলিভারি দিয়েছিল। পাবলিসিটি করার জন্যে একটা জাহাজ মাত্র ৪ দিন ১৫ ঘন্টায় পানিতে ছাড়া হয়েছিল! লিবার্টি শিপ-এর একটু ইম্প্রুভড ভার্সনের ৫৩৪ খানা ‘ভিক্টোরি শিপ’-ও তৈরি করা হয়েছিল ১৯৪৪-৪৫ সালের মাঝেই। এই ধরনের জাহাজগুলি প্রধানত মালামাল পরিবহণ করলেও বেশকিছু জাহাজ সৈন্য পরিবহণেও ব্যবহার করা হয়েছিল।
যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে কয়েক হাজার জাহাজ পুরোপুরি বেকার হয়ে যায়। কিছু কিছু জাহাজ নৌবাহিনী বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাজে ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত মার্কিন সরকার ৫০০ জাহাজ স্টোর করে রাখে। এই জাহাজগুলিকে এমনভাবে রেখে দেওয়া হয় যেন সর্বনিম্ন ক্ষয়ের মধ্যে এই জাহাজগুলি অনেকদিন টিকে থাকতে পারে। ‘ন্যাশনাল ডিফেন্স রিজার্ভ ফ্লীট’ নামে এই নৌবহরে বেশিরভাগ জাহাজই ছিল বাণিজ্যিক জাহাজ। যদি ভবিষ্যতে কোন ইমার্জেন্সি কাজে দরকার লাগে – এই কথা ভেবে এগুলিকে রেখে দেওয়া হতো। কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে ৫৪০টা জাহাজ কাজে লাগানো হয়েছিল। ১৯৫১-৫৩ সালে কয়লা এবং খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্যে ৬০০ জাহাজ ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪-এর মাঝে ৬০০ জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিল খাদ্যশস্যের ভাসমান মজুদ হিসেবে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে গেলে ২৫২টা জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭২টা জাহাজ। তবে ১৯৫০ সালে এই ফ্লীটে ২,২৭৭টা জাহাজ থাকলেও ২০০৭ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ২৩০-এ নেমে আসে। এই পুরোনো ‘অদরকারি’ জাহজগুলি রেখে দেওয়ার অর্থ মার্কিন সরকার চিন্তা করতে পারতো বলেই অনেক অর্থ খরচ করে হলেও জাহাজগুলিকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ধনী দেশ বলে এটা পেরেছে – এটা অনেকেই বলবেন। কিন্তু আসল কথা তো শুধু সেখানে নয়; তারা যে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোথাও ছাড় দেয়নি, এটা তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। তারা তাদের অনেক জাহাজই বহু বছর রেখে দিয়েছে – অর্ধশত বছর পেরিয়েও – আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেনি।
বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার চিন্তায় বাণিজ্যিক জাহাজের বহর এবং পুরোনো জাহাজের বহর আসা উচিত। অভ্যন্তরীণ জাহাজ তৈরি দেশের জাহাজ শিল্পকে এগিয়ে নেবে, কিন্তু দেশকে ম্যারিটাইম দেশে রূপ দিতে হলে সমুদ্রগামী জাহাজের বহরের বিকল্প নেই। দেশের শিপইয়ার্ডগুলি এখন সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরিতে যথেষ্ট পারঙ্গম। এটাই সময় সরকারের নীতি নিয়ে ভাবনার। আলফ্রেড মাহান যে পথের কথা বলেছেন, সে পথে অনেক কাঁটা থাকবে। শক্ত নেতৃত্ব না হলে দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য সবল নীতি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে না।